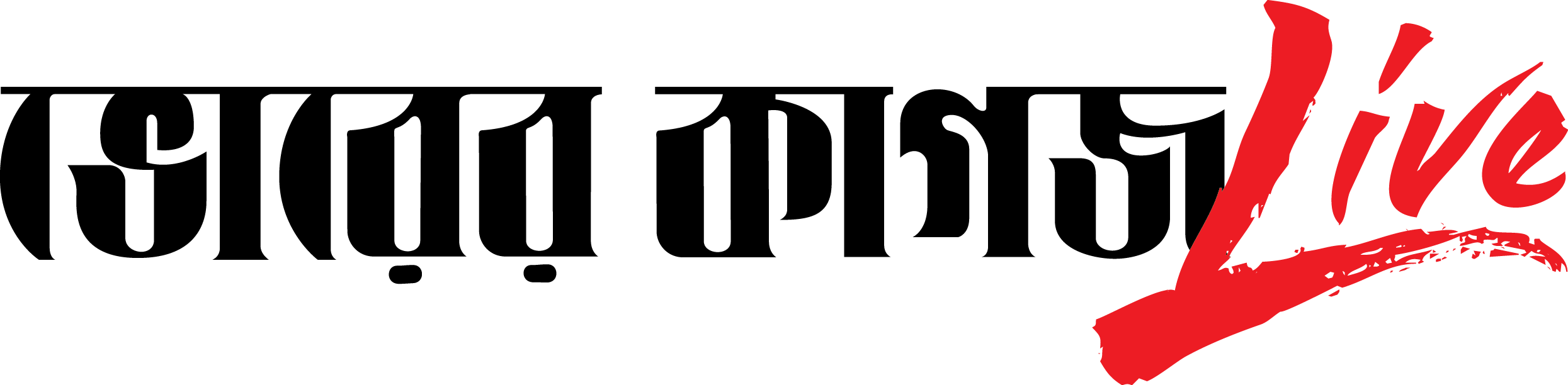বিরহের কথা সে লিখে পাঠাল
অমিয় দাশ, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে
প্রকাশ: ১৪ মে ২০২৪, ০৭:৪৩ পিএম

গল্প লিখেছেন ফার্মাসিস্ট অমিয় দাশ ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে
ইদানীং বীথি আর দীপ্ত দুজনেই হাইস্কুল পাশ করে কলেজে চলে যাওয়ার পর থেকেই তাদের দেখা সাক্ষাৎ খুবই কম হচ্ছে। দীপ্ত ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে, আর বীথি পড়ে ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষে। আন্তঃস্কুলের এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠানে ওদের দুজনের প্রথম পরিচয়। তারপর অল্প অল্প করে জানাশোনা থেকে বন্ধুত্ব। বছর খানেক আগেই বন্ধুত্বের গণ্ডী পেরিয়ে আরো গাড় মধুর সম্পর্কের দাগ ছুঁয়েছে।
দীপ্ত যখন কলেজের প্রথম বর্ষে, বীথি তখন হাই স্কুলের গণ্ডীটি পার হবে হবে। দীপ্ত কলেজ থেকে ছুটি-ছাটাতে বাড়িতে এলেই বিভিন্ন অজুহাতে দেখা হতো বীথির সাথে। দীপ্তদের বাড়ী বিথীদের বাড়ি থেকে বেশি একটা দূরে নয়, আবার তেমন একটা কাছেও নয়। সাইকেল চালিয়ে গেলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে যায়। স্মার্টফোনের বদৌলতে কোথায়, কখন দেখা হবে তা ঠিক করে নিতে তেমন বেগ পেতে হয় না।
দীপ্তর কাছে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাইকেল চালিয়ে বীথির কাছে যাওয়া যেন কয়েক মিনিটের মতো। বীথির কাছে যাওয়ার সময় তার সাইকেল যেন পঙ্খীরাজের মতো চলে। কিছু বোঝার আগেই সে হাজির হয়ে যায় আগে থেকে ঠিক করে রাখা জায়গায়।
বীথিদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছে। ওখানেই সাধারণত দেখা হয়। শীতকালে ওটাকে নদী বললে ভুল হবে। বলা উচিত স্থির হয়ে বসে থাকা একটা মরা নদী। কোথাও কোথাও তির তির করে সাপের মতো একটু একটু পানির প্রবাহকে নদী বলা চলে না। তবে কুল কুল শব্দটা বড় মায়াময়।
নদীর মাঝখানের দিকে তাকালে মনে হবে উঁচু-নিচু বালুর ঢিপি। যেখানে তির তির করে পানি বয়ে যাচ্ছে সেই ঢালু জায়গাটাতে দাঁড়ালে মনে হয় চারিদিকে বালুর ছোট ছোট টিলা। এসব টিলার আবার মালিক আছে। এলাকার গণ্যমান্য চেয়ারম্যান বা মেম্বর শ্রেণীর লোকজনের দখলে বালুর টিলাগুলি। টিলা করে রাখা, বিক্রি হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। বিক্রি ও ট্রাকের বোঝাই দেওয়ার কাজ চলে রাতের অন্ধকারে। ঠিক আইনসম্মত কাজ না কিনা, তাই। দিনে কেউ সাধারণত এ দিকটা মাড়ায় না।
দীপ্ত আর বিথী দেখা করে এই নদীর পাড়ে। তারপর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সাইকেলটা নিয়েই ওই বালুর টিলার মেইজে গিয়ে কোন ঘাসের উপর বসে গল্প করে। মাঝে মাঝে দীপ্ত চানাচুর ভাজা কিংবা বাদাম কিনে কাগজের প্যাকেটে করে নিয়ে আসে।
নদীর দুধারে অজস্র খেজুর গাছ আর শিমুল গাছ। খোলা জায়গা পেয়ে শিমুল গাছগুলো তাদের ডালপালা বিস্তার করতে যেন একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। খেজুর গাছ গুলোও কম যায় না। বাড়তে বাড়তে অনেকগুলো খেজুর গাছ এখন এত বড় হয়েছে যে গাছিরাও সাহস করে না রস সংগ্রহ করতে। নদীর মাঝখানে থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের মাঝে গাঢ় লাল রঙের শিমুল ফুলের ছলচাতুরী। এখানকার দুটো বড় বড় খেজুর গাছ নদীর ধার ঘেঁষে হেলে নদীর উপরে গা এলিয়ে আছে। এই খেজুরগাছ দুটো দীপ্ত ও বীথির খুব প্রিয়। মাঝেমাঝেই ওরা হেলে থাকা গাছের একটার উপর বসে গল্পগুজব করে। লোকজনের তেমন যাতায়াত নেই এদিকটায়। দু একটা জুটি দেখা যায়। তারাও সবাই একটা দূরত্ব রেখে বসে।
এবছর যোগাযোগটা সেভাবে আর হচ্ছেনা। বীথি একটি কলেজে পড়ে, যা রাজধানীর সেই ভিড় কোলাহল মুখর পরিবেশের একটা বড় কলেজ। কলেজের কাছেই তার বড় খালার বাসায় সে থাকে। বীথি একদিন দীপ্তকে বলেছে যে ওদের কলেজটার নাকি বেশ নামডাক। দুটো সেকশন আছে। ইংলিশ মিডিয়াম, আর বাংলা মিডিয়াম। বীথি অবশ্য বাংলা মিডিয়ামে পড়ে।
বীথির কলেজের ছুটি-ছাটার ব্যাপার গুলো বেশ গোলমেলে। শুধুমাত্র তিনটে ধর্মীয়, তিনটে রাষ্ট্রীয় ছুটি ছাড়া আর সব ছুটিগুলো দীপ্তর কলেজের ছুটির সাথে একদম মেলেনা। ফলে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি বেশ কিছুদিন। মাঝেমাঝেই বিথী বলে যে, থ্যাংকস টু গড ফর দা স্মার্ট ফোন। তা না হলে যে কি হতো? কিভাবেই বা যোগাযোগ হতো, ইত্যাদি।
প্রতিদিন না হলেও নিয়মিত ওদের টেক্সটিং বা খুদে-বার্তার আদান-প্রদান হয়। দুতিন দিন পর পর, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে। ভালই দিন কেটে যায় ওদের। কতো রকম ইমোজি ব্যবহার করে বীথি তার যেন ইয়ত্তা নেই।
দীপ্ত নাম শুনে যেমন মনে হবে সে সুদর্শন, মেধাবী, চটপটে, এককথায় স্মার্ট একটা কলেজ পড়ুয়া ছেলে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। দীপ্ত একটু মুখচোরা স্বভাবের। সাদামাঠাভাবে কথা বলে। কথা বলার সময় তেমন কোন নাটকীয় অঙ্গভঙ্গিও থাকে না। আর সব গুন থাকা সত্ত্বেও ওকে ঠিক স্মার্ট ছেলেদের দলে ফেলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেকেরই দ্বিমত হবে। অন্যদিকে বীথি অনেক চটপটে। লেখাপড়ায়ও ভালো। তা না হলে তো আর অত ভালো আর বড় একটি কলেজে চান্স পেত না। তবে ইদানীং কথার মাঝে ইংরেজি শব্দ, কখনো কখনো পুরো লাইনই ইংরেজিতে বলে। মনে হয় কোন ইংরেজি মিডিয়ামের সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ঘোরাফেরা বা আড্ডা দেয়।
কিছুদিন আগে বীথি খুব চাপাচাপি করে দীপ্তকে তার ফেসবুক ফ্রেন্ডস লিস্টে যোগ করে নিয়েছে। দীপ্ত ফেসবুকিং করে বটে, তবে অনর্গল বলে একটা কথা আছে, সেভাবে নয়। মাঝে-মধ্যে পড়ার ব্রেকে একটু দেখে নেওয়া, এই আর কি। ফ্রেন্ড লিস্টেও তেমন বেশি কেউ নেই। তাছাড়া সাথে সাথে দ্রুত মেসেঞ্জারের জবাব না পেয়ে ফ্রেন্ডলিস্টের বন্ধুরাও বোধ হয় দীপ্তকে ইগনোর করা শুরু করেছে।
এই গত কয়েকদিন যাবত বীথি বেশ মেসেজ করছে, সাথে ইমোজি পাঠাচ্ছে। কিছু কিছু ইমোজির মানে কি তার রহস্য ভেদ করতে দীপ্তকে গুগল করতে হচ্ছে। কাদের যে খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, যে গাদা গাদা ইমোজি বানায়! সেদিনই তো বিথী একটা ইমোজি পাঠিয়েছে, যা দীপ্ত বাপের জন্মেও দেখেনি। কি যন্ত্রণা। ইগনোর করারও উপায় নেই, আবার জানতেও ইচ্ছে করছে। গুগল করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করতেই সে দেখলো, সেই ইমোজিটির সম্বন্ধে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের বিভিন্ন মতামত। কেউ বলছে ইমোজিটির মানে হলো “মুচকি হাসি”, কেউ কেউ বলছে “হাল্কা হাসি”, আবার এক জায়গায় পেল “ছদ্মগাম্ভীর্যের সাথে হাসি”। কোনো মানে হয়? তার নিজের কোনো ধরনের হাসি আসা তো দূরের কথা, বিরক্তিতেই মনটা তেঁতো হয়ে গেলো। ফোন রেখে, কলেজের একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল তার দিকে মন লাগালো।
কয়দিন ধরেই বীথি তাকে খুব খোঁচাচ্ছে ফেসবুক মেসেঞ্জারে, যে তাকে একটা চিঠি লিখতে। ওরা একে অন্যকে এত মেসেজ লিখছে, মাঝেমধ্যে কথাও হচ্ছে, তথাপি চিঠিটা তার চাইই চাই। বলেছে যে, একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে প্রেমের চিঠি লেখে তাহলে যে রকম হবে, সেরকম। ব্যাপারটা সে একটু আধটু যে বোঝেনি তা নয়। তবে এমনও হতে পারে যে কোন বান্ধবীকে প্রেমের চিঠি পেতে দেখেছে। আজকাল যা হয়েছে না, শুধু অনুসরণ আর অনুকরণ। যেমন কেউ কাউকে সেলফি তুলতে দেখলো কি খট্টাশ করে নিজের ধামা সাইজের একটা ফোন বের করে ওর থেকে বেশি কয়েকটা সেলফি না তোলা পর্যন্ত পেটের মধ্যে বাডুর-বুডুর চলতেই থাকবে যেন।
অগত্যা মনের মাধুরী মিশিয়ে একটা চিঠি লিখল দীপ্ত। সময় করে চিঠিটা ছেড়েও দিল বীথির নতুন ঠিকানায়। বীথিকে চিঠি ছাড়ার কথা জানাতেই সে কমপক্ষে কুড়িটা প্রশ্ন ছুড়ে মারল। কবে লিখলো, কখন লিখলো, কিভাবে, কিসের খামে, কত বড় চিঠি, প্রেমের চিঠি না নরমাল চিঠি, মন থেকে লিখেছে কিনা, কবে পাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি আরো কত কি। দীপ্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো, কিছু ইচ্ছে করেই বলল না বা গুছিয়ে বলতে পারবে না বলে এড়িয়ে গেলো। বীথি তো আর ছেড়ে দেয়ার বান্দা না। এদিকে দীপ্তও বলছে না। এক পর্যায়ে কথোপকথনটা কথা কাটাকাটিতে পরিণত হলো। দীপ্ত আস্তে আস্তে বলে ফেলল,
-‘ও তুমি বুঝবে না। ওসব বলতে আমার যে বড়ো কষ্ট হয়।’
-‘আমাকে বলতে তোমার কষ্ট হয়? আচ্ছা অত আর কষ্ট করতে হবে না।’
বলেই ক্লিক। বীথি ফোনটা কেটে দিলো। “টা টা” পর্যন্ত বলল না। দীপ্ত বীথিকে কথার শেষে “বাই”’ বলে, আর বীথি ওকে বলে “টা টা”। মনটা বিষণ্ণ করে দীপ্ত অনেকক্ষণ বসে থাকলো। ভাবলো, সে নিজে এরকম কেন? কেন সে বীথির কাছে সবকিছু গুছিয়ে বলতে পারেনা? তার মনের আকাশে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি ভেসে উঠল।
মনে পড়ল গতবছর পহেলা ফাল্গুনের দিনটি। বীথি দীপ্তকে ওই নদীর পাড়ে আসতে বলেছিল ওদিনটায়। দিনটাতে প্রেমিকাকে ফুল দেয়া একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দেখা করতে আসার পথে দীপ্ত চেষ্টা করেও কি রকম ফুল নিয়ে যাবে ভেবে পায়নি। গোলাপ ফুল ছাড়া আর কিছুর কথা মনে আসেনি। কাছের বাজারে ফুলের একটা দোকানে গিয়ে দ্যাখে গোলাপ ফুল সব শেষ। কি করবে ভাবতে ভাবতে আসার পথে নাগালে পাওয়া যায় এরকম একটা শিমুল গাছের ডাল থেকে একটা শিমুল ফুল তুলে, পাশের একটা কলাগাছের থেকে কলাপাতা নিয়ে, তার মধ্যে মোড়ক করে এনে দিয়েছিল বীথিকে।
বীথি অবাক হয়ে দীপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘আমি মনে করলাম তুমি গোলাপ ফুল দেবে।‘
বলেই হি হি করে হেসে ফেলল।
-‘গোলাপ ফুল কিনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গোলাপ ফুল পাইনি।‘
-‘তাই বলে শিমুল ফুল আনলে? শিমুল ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটা ফুটেনিতো?’ বলেই ফুলটাকে পরখ করে দেখে নিয়ে বীথি বললো, ‘গাছ তলার থেকে কুড়িয়ে আনা মনে হচ্ছে না, একদম ফ্রেশ!‘
-‘হ্যাঁ, গাছ থেকে পেড়ে এনেছি। কাঁটা ফুটেনি।‘
তারপর নদীর দুই ধারের অজস্র শিমুল গাছ দেখিয়ে দীপ্ত বলেছিল, ‘ওই দেখো, নদীর দুধারের শিমুল গাছগুলোতে সবেমাত্র ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। তাতেই কত রক্তিম সুন্দর! এই লক্ষ শিমুল ফুলের একটা তোমাকে দিলাম!’
বিথী অবাক হয়ে মুখচোরা দীপ্তর মুখে কথার খৈ ফুটতে দেখে, তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আজ তোমাকে অনেক রোমান্টিক লাগছে!’
-‘তা জানিনা, তবে আজকে আমার মনটা অনেক ফুরফুরা রকমের ভালো লাগছে। তুমি সাথে থাকলে আমার সবকিছু কেমন যেন ভরা ভরা লাগে। তোমাকেও এই সুন্দর কমলা রঙের শাড়ি, আর খোঁপায় গাঁদা ফুলের মালা অনেক সুন্দর লাগছে!’
একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তারা বসেছিল অনেকক্ষণ। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে বীথি বলে উঠলো, ‘খেজুরের রস খাবো।‘
নদীর পাড় দিয়ে এক গাছি কাঁধে করে তার বিকেলের সংগ্রহের রসের ভাড় নিয়ে যাচ্ছিল বাঁশের চটা দিয়ে বানানো বাঁকে করে। বীথি তাকে দেখেই রস খাওয়ার কথা বলেছে। দীপ্ত দৌড়ে গাছির কাছে পৌঁছে, তাকে বলে কয়ে থামালো। ইশারা করে বীথিকে ডেকে কাছে আনলো। রাস্তাঘাটে এভাবে রস বিক্রি হয়না।গাছির কাছে গ্লাস না থাকায় তারা হাত পেতে রস খেয়েছিল, টিউবওয়েলের পানি খাওয়ার মত। গাছি রস হাতের উপর আস্তে আস্তে ঢেলেছিল রসের ভাড় থেকে। সে দাম নিতে চায়নি। তাও বিথী দশ টাকার একটা নোট বের করে জোর করে ধরিয়ে দিয়েছিল গাছিকে।
রস খেয়ে যখন ওরা বালুর টিলার চোরাগলিতে গেল, তখন সূর্য কেবল গাঢ় গোলাপি রং হয়ে আস্তে আস্তে অস্ত যেতে চলেছে। বিথীর মুখে রোদ পড়তেই মনে হচ্ছিল তার ঠোঁটের পাশ থেকে সোনালী রোদ চকচক করছে।
ওই চকচকে ভাবটা কেন? এটা বুঝতে দীপ্তই চকচকে জায়গাটাতে হাত দিয়ে আলতো করে স্পর্শ করল। বীথি কি বুঝল কে জানে? এগিয়ে এসে একটু উঁচু হয়ে দীপ্তর ঠোঁটের কাছে এলিয়ে দিল মুখটা। দীপ্ত একটা আলতো চুমু দিল। তারপর থুঁতনি ধরে বীথির মুখটা একটু তুলে পরপর ঘন ঘন কয়েকটা চুমু বসিয়ে দিল বীথির ঠোঁটে ও গালে। তারপর জিহ্বা দিয়ে নিজের ঠোঁট চেটে বলল, ‘মিষ্টি‘।
-‘তাই নাকি?‘ বলেই মুচকি হাসলো বীথি।
দীপ্ত এবার বীথিকে কাছে টেনে নিয়ে বীথির মুখ বিড়ালের মতো দুবার চেটে নিল। তারপর চকোলেট চুষে খাওয়ার মত চুক চুক শব্দ করে বললো,‘তুমি তোমার মুখের উপর শুকিয়ে যাওয়া খেজুরের রসের চেয়েও অনেক বেশী মিষ্টি!‘ বলেই একটু মুচকি হাসলো।
আর যায় কোথায়। বীথি দীপ্তকে প্রথমে একটু ধাক্কা মেরে, তারপর আরো সজোরে কাছে টেনে দীপ্তকে লম্বা একটা চুমু খেয়ে জড়িয়ে ধরে থাকলো। অনুভব করল একে অন্যের হৃৎস্পন্দন।পৃথিবীর সব শব্দ যেন থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। শুধু অনুভূত হল একে অন্যের হৃৎস্পন্দন, অনেকক্ষণ।
এই বালুর ঢিপির আড়ালেই তাদের প্রথম একে অন্যকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া। দুজনের কাছে জীবনের প্রথম মধুর, প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা। সারাজীবন মনে রাখার মত মধুর ঘটনা। জীবনের প্রথম চুমু সবার মনে থাকে। প্রকৃতির কাছে মন খুলে কিছু চাইলে, প্রকৃতি মনে হয় তা দেয়ার জন্যে ইশপিস করে, দিতে তার কার্পণ্য হয়না। সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়। এইতো দিনটা ছিল গত বছর বসন্তের শুরুতে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এক যুগ আগে।
বীথি কি অভিমান করলো, না রেগে গিয়ে ফোন হ্যাংআপ করে ব্রেকআপ করলো? আর হয়তো কখনো যোগাযোগই রাখবে না। মন খারাপ করে, ভাবতে ভাবতে দীপ্ত তার ফোনটা নিয়ে মেসেঞ্জারে বীথিকে মেসেজ টাইপ করা শুরু করল। একটা কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মেসেঞ্জারে এত বড় মেসেজ ধরছে না, ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব কথা বীথির জানা উচিৎ। দীপ্ত ভাবলো, একটা ডকুমেন্ট ফাইল বানিয়ে ইমেইলে অ্যাটাচমেন্ট করলে কেমন হয়? সে গুগল ডকে একটা ফাইল তৈরি করবে, যেটা কিনা অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে ইমেইল করতে পারে।
দীপ্ত তার ল্যাপটপ কম্পিউটার খুলে গুগল ডকে তার চিঠি লেখা, আর চিঠিটি ডাকযোগে পাঠানোর ঘটনাপ্রবাহ লেখা শুরু করলো। ফাইলটির নাম দিলো “তোমার অভিমান ভাঙাতে…” সে লিখলো-
প্রিয় দোয়েল পাখী,
তোমাকে লিখবো বলেছিলাম। তুমিও চেয়েছিলে যেন তোমাকে একটা চিঠি লিখি। কাগজের উপর, কলম দিয়ে হাতের লেখা চিঠি। সময়ের সাথে সাথে হাতে চিঠি লেখটাই মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে,মানে ক্লাউডে! সেটা তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে খুব অনুভব করেছি আমি। তোমাকে একটা খুব সাদামাঠা করে লিখেছি বটে, কিন্তু তার যে প্রস্তুতি আর ঘটনাপ্রবাহ, তার যে উত্তেজনা, সেটার অনেকটাই বাকী রয়ে যাবে যদি তোমাকে সেগুলো না বলি। চিঠি লিখতে গিয়ে যা যা করলাম, তার সাথে ভাবনাটাও তো গুরুত্বপূর্ণ আর বলা আবশ্যিক, তাইনা? এই যেমন ধরো, চিঠি লিখে সুন্দর করে ভাঁজ করতে হবে, সে ভাঁজটাও দুই ভাঁজ, তিন ভাঁজ, নয়তো চারভাঁজ। আবার মনে হল সুন্দর করে জাপানিজ ধাঁচে অরিগামী করে চিঠিটাকে একটা গোলাপ ফুল কিংবা একটা প্রজাপতির মতো বানাতে হবে।
মনে হয়েছিলো কাছে যদি খেজুরের রসের ঘ্রাণ বোতলে ভরা থাকতো, তবে তা একটুখানি চিঠিটাতে মাখিয়ে দিলে তুমি সে ঘ্রাণ নাকের কাছে নিয়ে, একদম চোখ বুজে, শুঁকতে আর হয়তো ভাবতে, আমাদের পরিচয় হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। মনে আছে? একটু ভালো করে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই, আমরা নদীর ধারের চিকন পথ ধরে একসাথে হাঁটতাম? যেখানে অনেক খেজুর গাছ ছিল। সেখানে রসের ভাঁড় ঝোলানো থাকত বেশকিছু খেজুর গাছে। খেজুরের কাঁটাওয়ালা বাইগো বা ডাল খণ্ড খণ্ড করে ভাঁড়ের মুখে খানিকটা বেরকরে ঢোকানো থাকতো। যেন কাঠবিড়ালি বা পাখী-পক্ষী ভাঁড়ের কানায় বসতে না পারে বা ভাঁড়ের মধ্যে ঢুকে রস নষ্ট না করে। বাতাসে ময়ময় করতো খেজুরের রসের মৃদু ঘ্রাণ।
আমি আর তুমি কতই না ওই সব পথে হেঁটেছি। নদীর পাড়ে দুটো খেজুর গাছ নদীর ধার ঘেঁষে নুইয়ে ঝুলে ছিল। আমরা সেই খেজুর গাছ দুটোর একটির উপর পা ঝুলিয়ে বসে কত আগডুম বাগডুম কথাই না বলেছি। কখনো মনেই হয়নি যে একদিন এত স্মৃতিময় মধুর হবে সে হাওয়া। আজ খুব টের পাই যে, মিস করছি সেই পথগুলো, সেই হাওয়া, সর্বোপরি তোমাকে। যদি সে ঘ্রাণ মাখিয়ে দিতে পারতাম, তুমি আলতো করে যখন নাকের ডগায় চিঠিটাকে ছোঁয়াতে। তখন আমার হাতের এই স্পর্শ তোমার গালে, ঠোঁটে এমনিতেই লাগতো। এটাও তো একরকম আদরের, আর ভালোবাসার ছোঁয়া।
কিন্তু দ্যাখো, এখন কি হয়েছে, লিখেছি বটে কিন্তু মনের মতো করে ছোঁয়া পাঠাতে পারিনি। ঠিকানা লিখেছি খামের উপর সুন্দর করে, যেন তুমি বুঝতে পারো কতই না যত্ন করে তোমাকে লিখেছি। তারপর অরিগামীর ভাঁজ এর চিঠিটা খামে পুরে, জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে, খাম বন্ধ করেছি। পানি দিয়ে নয়, জিহ্বার লালা দিয়ে! যেন আমার শরীরের দু একটা অনুকোষ তোমার কাছে পৌঁছায়। আমি না পৌঁছাতে পারলেও, আমার একটা দুটা ডিএনএ তো তোমার সাথে থাকলে মনে হবে আমি আছি তোমার বালিশের নিচে, সিন্ধুকে অনেকদিন, কিংবা ওয়েস্ট বাস্কেটে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সে যাই হোক আছি তো। শুনেছি যত্নে থাকলে ডিএনএ নাকি অনেকদিন বাঁচে।
তারপর জানো কি হয়েছে? আমি সময় করে পোস্ট অফিসে গেলাম। অলস পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে স্ট্যাম্প কেনার জন্যে পোস্ট অফিসে লাইনে দাঁড়ালাম। লাইনে আট-দশ জন লোকের পেছনে আমি দাড়িয়ে। কারো কাছে কোনো চিঠির খাম দেখলাম না। প্রায় সবার হাতেই কম বেশি নগদ টাকার গোছা, বান্ডিল দেখলাম। লোকজন কি কাড়িকাড়ি টাকা নিয়ে এসেছে আমার মতই স্ট্যাম্প কিনতে? নিজেকে আর একা মনে হলো না। দেখলাম সামনের লোকজন কেউই স্ট্যাম্প কিনল না। কেও টাকা জমা দিলো, কেউবা টাকা তুলল, গুনে গুনে হিসাব করে নিলো। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম পোস্টঅফিস এখন আর পোস্ট অফিস নেই। “পয়সা অফিস” হয়ে গিয়েছে। টাকা পয়সা ওঠানো, রাখা, লগ্নি করা ইত্যাদি কাজ চলছে ওখানে। কাউকে কেও মানি অর্ডার করে টাকা পাঠাচ্ছে না। এখন ব্যাংক আর পোস্ট অফিসের মাঝে তেমন কোন তফাৎ নেই বললেই চলে। প্রায় আশাহত ভঙ্গিতে ডাকটিকেট আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম বিজ্ঞ চেহারার পোস্টমাস্টার লোকটিকে। আমাকে বেশ পরখ করে দেখে নিয়ে সে একটা ড্রয়ার হাতড়ে একটা ময়লা পুরনো খাতা বের করে জিজ্ঞেস করলো,
-‘চিঠি কি দেশের ভিতরে, না বিদেশে যাবে?’
আমি খামটা একটু উঁচিয়ে দেখিয়ে বললাম,
-’দেশের ভেতরে।’
-’ও।’ বলেই একটা ডাক টিকেট এগিয়ে দিয়ে বিরক্তির সুরে বলল, ‘৫ টাকা খুচরা আছে? আমার কাছে খুচরা নেই।’
আমি আমার সঞ্চয় করা টাকা নিয়ে চিঠি পোস্ট করতে গেছি। সবই খুচরা টাকা, কয়েন, ইত্যাদি আমার পকেটে। আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। পোস্টমাস্টার একটা ডাকটিকেট এগিয়ে দিলো। ডাকটিকেটটা দেখে আমার ঠিক পছন্দ হলো না। কি সব হিজিবিজি, কিসের একটা ফটো যেন। ছাপানোটাও পরিষ্কার হয়নি। ঐ ডাকটিকেটের দাম অর্ধেক হওয়া উচিৎ। দামাদামি করার এখতিয়ার থাকলে, ঠিক জিগ্যেস করতাম যে অর্ধেক দামে ওই ডাকটিকেট আমার কাছে বিক্রি করবে কিনা। তোমার কাছে আমি জীবনের প্রথম চিঠি লিখছি। মনে রাখার মতো আর্টিস্টিক একটা ডাকটিকেট আঁটাতে হবে খামের উপর, যাতে ওটা দেখেই তোমার মন ভাল হয়ে যায়!
আমি জিজ্ঞেস করলাম,
-‘অন্য কোন ভালো, আরো ভালো ডিজাইনের স্ট্যাম্প আছে স্যার?”
নিরাশ ভঙ্গিতে নাকের উপর ঝুলে থাকা চশমার ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু না করেই পোস্টমাস্টার বললো,
-‘ওই তো হলো। ওটা লাগালেই সঠিক জায়গায় চলে যাবে। একটুও নড়চড় হবে না। শুধু ঠিকানাটা ঠিক থাকলেই চলবে।”
তবুও মনটা চাইছে একটা শাপলা ফুল কোন স্তব্ধ লেকে ভেসে আছে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত শিশির গালে নিয়ে, এরকম ছবিওয়ালা একটা ডাকটিকেট। নয়তো একটা সাদা ধবধবে বলাকা গলাটা একদম সামনে বাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে, যেন দূর থেকে, অনেক উপর থেকে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে, এরকম একটা স্ট্যাম্প পেলে ভালো হতো। বললাম,
-‘তবুও দেখুন না একটু স্যার।’
আমার আকুতি হয়তো সে বুঝতে পারল। বললো,
-‘এই যে দ্যাখো। আর এই এক রকম আছে। একটা খালি গায়ে গাড়িয়াল, তার কাদায় আটকে থাকা গরুর গাড়ির চাকা ধরে ঠেলে কাদা থেকে গাড়ীটাকে সামনে আগানোর চেষ্টা করছে।’
বলেই শুধু হাত গলানো যায় এরকম জংধরা লোহার গ্রীলের ফুঁকো দিয়ে একটা স্ট্যাম্প এগিয়ে দিলো আমার সামনে। বললাম,
‘হয়েছে, বেশ পছন্দ হয়েছে।’
হেসে সঞ্চয় করা টিফিনের পয়সার থেকে দাম শোধ করে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ ডাকটিকেটটার দিকে। ভাবলাম, আচ্ছা এই গরুর গাড়ী, গরু, গাড়িয়াল, এসবের মধ্যে কোনটা আমি? কাদা, গরুর গাড়ী, নাকি গাড়িয়াল?
পোস্টমাস্টার বলল,
-‘স্ট্যাম্পটা খামে লাগিয়ে আমার কাছে দিতে পারো, আমি এখানেই ওই ডাকের বস্তায় দিয়ে দিব। ঠিক চলে যাবে। ঠিকানা লেখা হয়েছে? ঠিকানা লেখা না হলে, ঠিকানা লিখে, ওই লাল ডাকবাক্সেও ফেলতে পারো।’
আমি ইতস্তত করে বললাম,
-‘না, হ্যাঁ ঠিকানা লেখা হয়েছে। আর একটু দেখে নিই।’
বলেই ফুঁকোর কাছ থেকে সরে এলাম। তোমার কাছে এ চিঠি যাবে, কত হৃদয়ের মাধুরী, আমার ডিএনএ মিশিয়ে লিখেছি চিঠিটি। এ ভালোবাসা ঐ বস্তায় এখনই ভরতে মন সায় দিচ্ছিলো না। এ চিঠি আমি আস্তে করে আলগোছে ওই জবা ফুলের মত টকটকে লাল ডাকবাক্সে রাখবো। যাতে আমার প্রতিটি ডিএনএ দম বন্ধ হয়ে না যায়। চিঠিটা পরে তো বস্তায় ভরবেই। সে ঠিক আছে। তাছাড়া মনে সন্দেহ হলো, পোস্টমাস্টারের হাতে খামটা দিলেই হয়তো সে পরখ করে তোমার ঠিকানা দেখবে। তোমার ঠিকানা দেখবে চশমার ভেতর দিয়ে, তারপর চশমার বাইরে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবে,
-‘কে হয়?’
আমি তখন কি বলবো? আমার কে হয়? তাই তো, আসলে তুমি আমার কে হও গো?
আমি তো কিছুই বলতে পারব না। শুধু বুকের মাঝে একটা ধক্-ধক্, ধক্-ধক্ শব্দ হবে। গলার শব্দ নিঃশব্দ হয়ে যাবে। জানো, এসব জায়গায় আমি কিচ্ছু বলতে পারি না। আমাকে প্রকাশ করতে পারিনা। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বরফের মত জমে যায়। পরে সেই বরফ গলে বটে, কিন্তু ততক্ষণের হয়ত দৃশ্যপটই পরিবর্তন হয়ে গেছে।
পোস্টমাস্টার আমার নীরবতা দেখে আরও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল,
-‘আত্মীয়?’
আমি বললাম,
-‘হ্যাঁ।’
বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল যে, ‘আমরা আর জন্মে সাথী ছিলাম। আমার পরম আত্মার আত্মীয়।’
তা কি আর বলা যায়? এটা বললেই পোস্টমাস্টার হয়তো আমাকে পাগল বলে পরে চিঠিটা ঠিক খুলে পড়বে। পড়ে হয়ত অনেক হাসাহাসি করবে। আর গন্তব্যে পাঠাবেই না। একবার খাম খুললে সে তার অপরাধবোধ বশতঃই পাঠাবে না, এটা একদম নিশ্চিত।
না থাক, তাই ভেবে ওখান থেকে সরে এলাম।
আমি বললাম,
-‘আচ্ছা, ঠিকানা চেক করে দেখে লাল ডাকবাক্সে ফেলব।’
চিঠিটা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে তো? আবার একটু হাত, চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম। চিঠিটা আবার ভালো করে দেখে নিলাম। কোন রকম ভুলভ্রান্তি হওয়া চলবে না। ভুল হলেই এই খামটা ভর্তি অনেক কথা তোমার কাছে পৌঁছুবেই না। হারিয়ে যাবে। কোথায় হারিয়ে যাবে তাও জানিনা। হয়তো নিরুদ্দেশের চিঠি গুলোর মতন পোস্টমাস্টার কেজি দরে ওই পুরনো বই-কাগজ কেনার ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দেবে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে হাত বদল হয়ে গ্রামের হাটের ওই চানাচুর, ছোলা বা বারোভাজার দোকানদারের কাছে চলে যাবে। আমার চিঠি হয়ে যাবে একটা বারোভাজা খাওয়ার খিলি পাত্র। আমার চিঠি তোমার পরিবর্তে দেখবে তৃপ্তি করে খাওয়া কোন কিশোর কিশোরীর, কিংবা লোকের তৃপ্তিতে ভরা মুখ। চিঠিটা হয়তো ভাববে কি এসে যায়? কারো একটু হাসিমুখ তো দেখতে পেয়েছে, সেটাই কম কি? সবাই কি আর সবার মনে হাসি ফোটাতে পারে বলো? তারপর চিঠিটাকে কি করবে কে জানে? হয়তো আমার আঁকা দোয়েল পাখীর ছবিটা দেখে সন্দিহান হয়ে কাগজটা পড়ে দেখবে। ভাববে কতইনা মনের আকুতি লুকিয়ে আছে এই চিঠিতে। হয়তোবা ভাববে, বিশাল একটা ঢং!
চিঠিটি লেখা হয়েছে তোমাকে আমার দেয়া ছদ্ম নাম “দোয়েল পাখী”কে উদ্দেশ্য করে। তুমি যে নামে গোপনে আমাকে ডাকো, সে নামটা লিখেছি একদম শেষে। লিখেছি, “ইতি, শুধু তোমার,বাবুই”, তোমার দেয়া সেই গোপন নামটা। জানো, তোমার দেয়া ওই “বাবুই” নামটা আমি অনেক অনেক ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি। আমি চাইনা এ জীবনে আর কেউ আমাকে ওই নামে ডাকুক।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,
‘নামেই কিবা আসে যায়,
যে নামে ইচ্ছা
সে নামে ডাকিও আমায়’।
কবি যাই বলুক না কেন, তোমার দেয়া “বাবুই” নামে তুমিই শুধু আমাকে ডাকবে। তোমারই শুধু অধিকার আছে আমাকে ওই নামে ডাকার। পৃথিবীর সব মানুষ আমাকে যে নামে খুশি ডাকুক, আমি শুধু ওই নামটা তোমার কাছ থেকেই, তোমার কণ্ঠেই শুনতে চাই। এটা কি খুব বেশি চাওয়া বলো? আমিতো প্রকৃতির কাছে, কারো কাছে টাকা পয়সা, কোন মূল্যবান জিনিস কিছুই চাইছি না। শুধু ওই নামটা এইতো।
জানো, চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে, খামটা বন্ধ করার পর মনে হল একটা ভুল হয়ে গেছে। সেদিন একটা গল্প পড়ছিলাম জগৎ বিখ্যাত যোদ্ধা ও ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্বন্ধে। অনেক কিছুই করেছেন নেপোলিয়ন তার জীবনে। কিন্তু তার একটা বিশেষ বিষয় আমার খুউব মনে ধরেছে। তার স্ত্রী জোসেফিনকে সে চিঠি লিখতো যুদ্ধে থাকা অবস্থায়ও। সে ছিল খুব সাহসী যোদ্ধা। ফ্রান্সকে সে যে কোন আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। অনেক বিজয় ছিল তার ঝুলিতে। একবার নেপোলিয়ন একটা যুদ্ধে হেরে যায়। সবাই কি আর সব সময় জেতে বলো? জয়-পরাজয় নিয়েই তো আমাদের জীবন। তারপর তাকে বেশ কিছু রক্ষীসহ একটি বিরান দ্বীপে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়। স্ত্রীকে সে সাথে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু অনুমতি মেলেনি। সব বিজয়ের যত আনন্দ ছিল তার জীবনে, স্ত্রী-বিরহের দুঃখ তাকে তার চেয়েও বেশি দুঃখ ভারাক্রান্ত করেছিল। সে তার নিজের জীবনের চেয়েও তার স্ত্রীকে বেশী ভালোবাসতো।
তারও আগে একবার ইটালিয়ানদের সাথে যুদ্ধ বাধলো নেপোলিয়ন বাহিনীর। সে এক ভীষণ ভয়াবহ যুদ্ধ। যুদ্ধ ময়দানে তার সাথে হাজারো সেনা থাকলেও, সেই বিরান প্রান্তরে তার খুব একা আর নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এমন যদি হতো যে, তার স্ত্রী জোসেফিন যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাথে আছে। তাহলে অতি সহজেই সে মনে হয় যুদ্ধে জয় আনতে পারবে। কি অদ্ভুত ভাবনা, তাইনা? যুদ্ধক্ষেত্রে আবার কেউ তার স্ত্রীকে নিয়ে যায় নাকি? এ তো আর মধুচন্দ্রিমা না! এ হলো জীবন মৃত্যুর খেলা। সেখানে ভয় করলে বা বেখেয়াল হলেই মৃত্যু অনিবার্য। এমন খেলা যে, হয় মারবে, নয় মরবে। তবুও নেপোলিয়ন যুদ্ধের মাঝে বিশ্রাম বা ঘুমের যে একটু সময় পেতো, তখনই সে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখত। অনেক ভালবাসায় মোড়া সে চিঠিগুলো।
এইতো সেদিন খবরে দেখলাম, নেপোলিয়নের লেখা একটি চিঠি কোন এক সংগ্রাহক ৫ লক্ষ ইউরোতে বিক্রি করেছে অন্য কোন এক সংগ্রাহকের কাছে। টাকায় হিসেব করলে আজকের দরে সেটা প্রায় ছয় কোটি টাকারও একটু বেশী, আর রুপিতে প্রায় সাড়ে চার কোটি রুপি। বিরাট এক নিলাম হাউস চিঠিটা নিলামে তুলেছিল।
সে যাকগে, ভালোবাসা বিক্রি হোক, আর চিঠি বিক্রি হোক, তাতে কার কিই বা এসে যায়? যে বিশেষ ব্যাপারটা আমার মনে ধরেছে তা হল, নেপোলিয়ন তার স্ত্রীকে চিঠি লেখা শেষ হলে তার ঘাড়ের ঘর্মাক্ত এলাকায় চিঠিটা বার কয়েক ঘষে ঘাম লাগাত। তারপর চিঠিটা খামে পুরে, ভালমতো খাম বন্ধ করে, পাঠাতো তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। জোসেফিনও জানতো ব্যাপারটা। চিঠি পেলেই সে চিঠিটাকে কি করতো তা তো বুঝতেই পারছ। জোসেফিন চোখ বন্ধ করে, চিঠিটাকে তার নাকের কাছে এনে প্রাণভরে তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর গায়ের ঘ্রাণ নিতো। তারপর চিঠিটা পড়তো। নেপোলিয়ন কেন এরকম করতো তা কারো জানা নেই। কেউ কেউ এটাকে অত্যধিক ভালোবাসা, আবার কেউ কেউ এটাকে নিরাপত্তা হিসাবে মনে করে। রাজার চিঠি বলে কথা! হাতের লেখা নকল করে যদি কেউ উল্টোপাল্টা লিখে জোসেফিনকে পাঠায়, কিংবা কোন শত্রুপক্ষ যদি সুবিধা নেয়ার জন্য কৌশল করে ক্ষতি করার জন্য কোনো চিঠি পাঠায় তাহলে? হাতের লেখা নকল করতে পারলেও, গায়ের ঘ্রাণ তো আর নকল করতে পারবে না, বলো? আর সেটা তো নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডের ঘ্রাণ! জোসেফিনও চিঠির গন্ধ শুঁকেই যাচাই করতে পারত যে এটা তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর পাঠানো চিঠি কিনা।
তোমাকে লেখা চিঠির খাম বন্ধ করার পর মনে হয়েছিল যে আমিও নেপোলিয়নের মত করে আমার ঘাড়ের ঘাম মাখিয়ে তোমাকে চিঠি লিখলে কেমন হতো? ততক্ষণে চিঠির খামটা বন্ধ করেছি। ততক্ষণের চিঠির খামের আঠা তার কাজ ঠিকমতোই করে ফেলেছে। খামটা খুলতে গেলেই হয়তো ছিঁড়ে যাবে খামের পেছনের ফ্লাপটা। অনেক সময় আঠা শুকালে, জোড়া দেয়া জায়গাটা শক্ত কড়কড়ে হয়ে আলাদা হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখলাম তা হয়নি। ইচ্ছে আছে আগামী চিঠিতে তোমাকে আমার ভালোবাসার ঘ্রাণ পাঠাবো। আরেকটা জিনিসও করতে পারি। একদিন তোমাকে একটা ম্যাজিক চিঠি পাঠাবো। চিঠিটি হবে এরকম যে, সাধারণভাবে তুমি লেখাগুলো কিছুই দেখতে বা পড়তে পারবেনা। চিঠিটা যখন পানিতে ভেজাবে, শুধুমাত্র তখনি সব লেখা ফুটে উঠবে, সব রঙের কাজ তুমি দেখতে পাবে।
তোমার সাথে এসব প্রসঙ্গে এত কম কথা হয়েছে যে বলাই হয়নি। অবশ্য কাউকেই কখনোই বলা হয়নি। বলার কথাও না, বারণ আছে। তবে তোমাকে বলতে পারি। তুমি তো আমাদের এসব গোপন কথা আর কাউকে বলবে না, তাই না? তোমার মনে আছে কিনা জানিনা, আমাদের কয়েক বাড়ি পরে, ঈশরাত নামে একটা আপু ছিল। বলেছিলাম কখনো? যাহোক, ঈশরাত আপু বেশ সুন্দর ফর্সা, লম্বা আর গোলগাল দেখতে। তোমার মত তারও ঠোঁটের পাশে বড় একটা তিল ছিল। ঈশরাত আপুর তিল বিশ হাত দূর থেকেও দেখে বোঝা যেত, ঠিক তোমার মতো। ঠোঁটের পাশে তিল থাকলে নাকি মানুষ অনেক ভালোবাসা পায় শুনেছি। ঈশরাত আপু আমাকে খুব পছন্দ করতো, স্নেহ করতো। আমিও তাকে আমার বড় আপার মতই বা তার চেয়ে একটু বেশিই ভালবাসতাম।
মাঝেমধ্যেই ওনাদের বাড়ির ওদিকে গেলেই ডেকে নিয়ে আমার সাথে অনেক কথা বলতো, গল্প শোনাতো। আমি বেশ বুঝতাম সেসব বিভিন্ন গল্প। ঈশরাত আপুর গল্পের বই পড়ার খুব বাতিক ছিল। এর জন্য অনেক গালমন্দও খেতে দেখেছি। বড়দের গল্পকে খুব সুন্দর করে ছোটদের মতো করে আমাকে শোনাতো, নাকি বানিয়ে বানিয়ে বলতো কে জানে? মাঝেমধ্যেই আমাকে বাতাসা দানাদার জাতীয় মিষ্টি খেতে দিত। বড় লক্ষী মেয়ে ছিল ঈশরাত আপু। মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করে পাশ করার পর উচ্চমাধ্যমিকে পড়তো। দ্বিতীয় বর্ষ। ঈশরাত আপুর আব্বার খুউব ইচ্ছে এই লক্ষী মেয়েটাকে অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করাবে। অনেক বড় করবে, মেয়েটি বড় চাকরি করবে। ঈশরাত আপু পরিপাটি পোশাক পরে, লাঞ্চবক্স নিয়ে বড় কোন কোম্পানির অফিসারদের বাসে চড়ে অফিসে যাবে। অফিসার মিস ঈশরাত জাহান যখন মাথা উঁচু করে অফিসার-বাসে উঠবে, দেখতে কতই না ভালো লাগবে। বুকটা তার গর্বে ভরে উঠবে। একদিন বারান্দার একটা বেঞ্চিতে বসে ঈশরাত আপুর আব্বা বাটি ভর্তি মুড়ি পাটালী গুড় দিয়ে খেতে খেতে ঈশরাত আপুকে বলছিল। আমিও মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম ঈশরাত আপুর সাথে সাথে। এও দেখেছিলাম, ঈশরাত আপুর আম্মা গজ-গজ করে রান্নাঘর থেকে কি যেন নেওয়ার জন্য এ ঘরের দিকে আসার পথে বলেছিল বেশ কিছু কড়া কড়া কথা। সব মনে নেই, তবে বেশ কিছু কথা এরকম,
‘আফনের এইসব আজব হতা বাত্তা আমাগো সাইজত ন। মাইয়াডা বিয়ার উপুযুত্তু হইছে। ভালো এ্যাড্ডা পুলা দেইখ্যা বিয়া দিয়া দ্যান ছাই।’
ঈশরাত আপুর মামা বাড়ি অন্য কোন জেলায়, তাই তার আম্মা এখনও ওইখানকার মতো করেই কথা বলে। দুএকটা কথা বাদে আর সব কথা বুঝতে তেমন অসুবিধা হয় না আমার।
খুব নরম সুরে অনেক আদরের গলায় ঈশরাত আপুর আব্বা বললেন,
‘হবে, হবে। বিয়ে-শাদিতো হবেই। এত তাড়াহুড়া করার কি আছে? পড়াশোনা শেষ করুক, তারপর দেখা যাবে।’
বলে মচমচ করে আনমনে কোন এক অচিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে মুড়ি চিবোতে লাগলেন। মনে হয় এই মচমচ শব্দেই আম্মা আরো রেগে গেলেন। গলা আরো চড়িয়ে বললেন,
-‘নেহা ফরা হিগ্গ্যা আমাগো মাইয়া এক্কেরে জচ ব্যারেস্টার হইবো।’ বলেই মাথা ঝাঁকি দিলেন।
-‘জজ ব্যারিস্টার না হলেও অফিসার হবে। বুঝলে, অফিসার।’
ঈশরাত আপুর মা অপ্রয়োজনীয় ভাবে ইচ্ছা করেই রান্না-বান্না করার কিছু তৈজস, হাতা বা খুন্তি দিয়ে একটু বেশি শব্দ করে কড়াই বা হাড়িতে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন,
-‘আমার এই যে কিলাশ ফাইপ ফাশ কইরাই বিয়া অইলো। আই কি খারাপ আচি নি? নিহাফরা হিগ্যা হের কি আর দুইডা বেশী চুক গজইতো?
ঈশরাত আপুর আব্বা অপলকে চেয়ে থাকে ঈশরাত আপুর দিকে। অনেক আদর আর প্রশান্তি তার চোখে। আম্মা ক্ষান্ত দেয় না। তিরস্কারের সুরে বলে,
-‘মাইয়া অপিচার হইবো। তাইলেই হইচে। গরীপের আবার ঘুড়া রুগ।’
কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু মচমচ মুড়ি খাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না। সবাই নিশ্চুপ।
ভাবলাম ঝড় মনে হয় থামল। কিন্তু তা হলো না। নিজেকে নিজে বলার মতোই আম্মা গজ-গজ করলেন,
-‘ওই পাড়ার মেম্বর ছাব যে ডাক্তর ফুলাডার হম্বন্ধ আইনলো, হেইডাও সাফ্ না কইরা দিলো। ফুলাডা নাহি দ্যাখতে কালা। ডাক্তর মাইন্সের আবার কালা আর ধলা কি? ডাক্তর তো ডাক্তরই। হেরপর আরো কত কি? ফুলা নাহি হাতুইররা ডাক্তর। হেইতো আর হাকিমী, কবিরাজী, ঝাড়ফুক্ কইত্তো ন। ডাক্তর ফুলা। ব্যাবাকে না কইরা দিলো। আমার কপাল!’
ঠাশ ঠাশ দুটো শব্দ এলো। মনে হয় ঈশরাত আপুর আম্মা কপাল চাপড়ালেন। আমার মনে হচ্ছিলো আরো ঝড় আসছে।
কিছু বোঝার আগেই ঈশরাত আপু আমাকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, ‘দীপ্ত, তুই এখন বাড়ি যা, কাল বিকালে আসিস্।’
আমি হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়লাম। ফিস্ ফিসিয়ে বলল, ‘আসিস্ কিন্তু।’
আমি ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে চলে এলাম। আসার পথে খুব মনে হয়েছিল, আচ্ছা, ঘোড়ারোগ কি রোগ? ঘোড়ারোগ হলে কি হয়? গরীবদেরই কি ঘোড়ারোগ হয়? শুনেছি ঘোড়ারা নাকি রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়। গরীবের ঘোড়ারোগ হলে কি মানুষ বিছানায় আর শুতে পারেনা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়? আবার মনে হয়েছিল ঈশরাত আপুর মনে হয় ওই ডাক্তার ছেলেটার সাথেই বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।
ডাক্তার জামাই নিশ্চয়ই ঘোড়ারোগের একটা ওষুধ দিতে পারবে। যদি ঈশরাত আপুর আব্বার ঘোড়ারোগ হয়েই থাকে।
পরের দিন বিকেলের পড়া শেষ করে আমি ঈশরাত আপুদের বাড়ীতে গেলাম। আপু যেতে বলেছিল, হয়তো বাতাসা বা দানাদার দিতে পারেনি ঝগড়াঝাঁটির তাণ্ডবে, তাই ডেকেছে।
এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিকেল বেলায় আমি ঈশরাত আপুদের বাড়িতে ঢুকলাম। উঠান পর্যন্ত এলাম বটে, তবে বেশ ভয়ে ভয়ে। আস্তে আস্তে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাঁটছিলাম, যেন কোন শব্দ না হয়। গতকাল যে একটা তাণ্ডব দেখে গিয়েছিলাম, তা কোথায় গড়ালো কে জানে? বুকের মধ্যে একটা ভয় এজন্যে, হয়তো ঈশরাত আপুর মা আমাকে বারবার ওদের বাড়িতে আসতে দেখে ধমকিয়ে বলবে,
‘এই তুই আবার আইছস্’?
ঈশরাত আপুকে আবার ধমকাবে। হয়তো বলবে,
‘তুই এই ফুলাডার লগে কি পুটুস্ পুটুস্ করোচ্? আয় এইহানে, এই থাল-বাসন গুলো ধো। সংসারের এট্টু কামে লাগ’, ইত্যাদি।
নাহ্, আমি ঈশরাত আপু ছাড়া আর কাউকেই ওদের বাড়িতে দেখলাম না। ঈশরাত আপু একা একা বারান্দায় বসে, কাগজ কেটে কি যেন একটা ডিজাইন বানাচ্ছে। আমি আবার ভয়ে ভয়ে ওদের রান্না ঘরের দিকে তাকাতেই ঈশরাত আপু নাক দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করে হেসে বলল,
-‘ভয় নেই রে দীপ্ত ! সবাই শান্ত হয়েছে। আব্বা বাজারে গেছে। আর আম্মা ওই বাড়ির কাকীর সাথে গল্প করতে গেছে।’
বলেই তার কাগজ কাটায় মনোনিবেশ করল।
আমি জিজ্ঞেস করলাম,
-‘এগুলা কি করছো ?’
ঈশরাত আপু বলল,
-‘এটা আমার কলেজের পড়াশোনার ব্যবহারিক কাজ। একে বলে প্রজেক্ট। ড্রয়িং করার মত, এটা সুন্দর করে বানিয়ে প্রফেসর স্যারের কাছে জমা দিতে হয়।’
আমি ঠিক বুঝলাম না। বললাম,
-‘পরীক্ষার খাতা জমা দেয়ার মত?’
-‘হ্যাঁ, সেরকম। যার প্রজেক্ট বেশি সুন্দর হবে, সে বেশি নম্বর পাবে।’
-‘পরীক্ষার খাতা জমা দিলে আমার স্যারেরা খাতার উপর লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে টিক চিহ্ন দেয় বা নম্বর লিখে দেয়। এগুলোর নম্বর কোথায় দেয়? ওই কাঁটা কাগজের উপর কোথাও টুক করে লিখে দেবে?’
-‘তুই তো ভারি চিন্তাবিদ! এজন্যেই তো তোর সাথে গল্প করে আমি খুব মজা পাই। আমার স্যারেরা ক্লাসের সবার নামের যে লিস্ট আছে তার মাঝে আমার নামের পাশে একটি নম্বর বসিয়ে দেয়।‘
-‘তুমি জানবে কিভাবে তোমার নম্বর কত?’
-‘সেই কাগজের লিস্টটা সামনের বেঞ্চের কোনায় বসা প্রথমজনকে গলিয়ে দেয়। প্রথম জন তার নাম খুঁজে নম্বর দেখে টুকে নেয়। তারপর সে দ্বিতীয় জনকে কাগজটা দেয়। তারপর তৃতীয় জনকে। এমনিভাবে ক্লাসের শেষ বেঞ্চি অবধি সে কাগজ চলে যায়।’
মনোযোগ দিয়ে শুনে বিষয়টা অনেক ভালো লাগলো বটে।
কিন্তু মনের মধ্যে একটা খচ্ খচ্ অশান্তি বয়ে যাচ্ছিল আমার। বললাম,
-‘এ তো বেশ সময়ের ব্যাপার। ক্লাশের প্রথম বেঞ্চ থেকে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত যেতেই তো ক্লাশের সময় অনেকটাই পার হয়ে যাবে।’
হেসে ঈশরাত আপু বলেছিল,
-‘তুই বড় হলে বুদ্ধিজীবী হবি, বুঝলি?’
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম,
-‘বুদ্ধিজীবী কি? তারা কিসের অফিসার? জানি তুমি অনেক পড়ে অফিসার হবে, বড় মাইনে পাবে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কোথায় চাকরি করে?’
-‘বুদ্ধিজীবীরা হলো বুদ্ধির ভাণ্ডার। ওরা বুদ্ধি বেঁচে খায়।’
আমি কিছু না বুঝেই ঈশরাত আপু্র প্রজেক্ট বানানো আর তার কাজের একাগ্রতার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমিও প্রজেক্ট করব। ঈশরাত আপুর মত এরকম কাগজ কেটে সুন্দর ডিজাইন বানাবো। আমিও অফিসার হবো, বুদ্ধিজীবী অফিসার।
একসময় ঈশরাত আপুর প্রজেক্ট করা শেষ হলো। সুন্দর একটা ডিজাইন। ঈশরাত আপু ডিজাইনটি হাতের উপরে রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল। কিছু বুঝলাম, বেশিরভাগই বুঝলাম না। তারপর ওটা ধরে ঘরে রাখতে গেল। ঘরে রেখে হাতের উপর একটা কাগজে করে কয়েকটা চিনির গজা এনে হাসিমুখে আমার হাতে দিলো। গজা আমার খুব পছন্দ। আমি ঈশরাত আপুর শিষ্য হয়ে গেলাম। গজা খেতে খেতে তারপর আমরা এই গল্প, সেই গল্প, একথা-সেকথা কত কি বললাম, শুনলাম। কথার ফাঁকে ঈশরাত আপু আমাকে জিজ্ঞেস করল,
-‘হ্যাঁরে দীপ্ত, তুই কি গোপন কথা গোপন রাখতে পারিস?’
আমি অবাক হয়ে বললাম,
-‘বারে, গোপন কথা তো গোপনই। তার আর রাখা বা ফেলার কি আছে?’
ঈশরাত আপু উৎসাহের সাথে বলল,
-‘আছে, আছে। গোপন কথা হলো নিঃশ্বাসের মতো। একবার বুকের মাঝে নিলি মানে আর বের করা যাবে না। বড় নিশ্বাস নিয়ে পানিতে ডুব দেওয়ার মতো। দম নিয়ে ধরে থাকতে হবে, ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তবেই সেটা গোপন থাকলো, বুঝলি?’
-‘হুম। আমার তো কোন গোপন কথা নেই। কেউ আমাকে গোপন কথা বলে না।’
-‘আমি তোকে প্রথম একটা গোপন কথা বলব। তোর জীবনের প্রথম গোপন কথা, বুঝলি?’
-‘আচ্ছা’
-‘দম নিয়ে গোপন কথাটা বুকের মাঝে আটকে রাখতে পারবি?’
-‘পারব।’
বলেই মাথা নেড়ে, বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আমি ঈশরাত আপুকে কথা দিলাম। এবার ঈশরাত আপু এদিক ওদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে তার একটা বইয়ের মলাটের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে আমাকে দিল। বলল,
-‘এটা তোর প্যান্টের পকেটে রাখ। সাবধানে রাখিস্, দলিয়ে মুচড়িয়ে ফেলিস না। খামের ভিতরে একটা ডিজাইন আছে ভাঁজ করা। ওটা যেন ভাজ করা একটা প্রোজেক্ট। ঐরকম।’
বলেই ঘরের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে সদ্য তৈরি করা প্রজেক্ট ডিজাইনের কথা মনে করিয়ে দিল।
-‘তুই এটাকে ও পাড়ার লোকমান ভাই আছে না? উনাকে দিবি।’
-‘আচ্ছা।’
বলেই আমার একটু মনটা আন্দোলিত হলো। একটু ভয়ও হল। জিজ্ঞেস করলাম,
-‘লোকমান ভাই যদি বাড়িতে না থাকে? তাহলে কি করব?’
-‘লোকমান ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। উনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে হেটে যাবি। যদি দেখিস ওনাকে, তবে বলিস যে উনার একটা জিনিস তোর কাছে আছে। খামটা বের করবি না যেন আগেভাগে।’
-‘আচ্ছা।’
আচ্ছা বললাম বটে, কিন্তু ওই শেষ কথাটা -”খাম টা বের করবি না যেন আগেভাগে” মনে করে আমার বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো ।
ঈশরাত আপুকে কথা দিয়েছি। আবার গোপন ব্যাপারটা গোপন রাখতে না পারলেও বেশ একটা ঝামেলা হবে বলে মনে হল। কিন্তু যে আমাকে এত আদর করে, বসে আমার সাথে কথা বলে, অনেক গল্প করে, তার এটুকু উপকার করতে পারলে ভালই হবে। তাছাড়া বাতাসা, গজা, দানাদার, গুড়ের পাটালী, ইত্যাদি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা হলো না। খামটা ধরে উঠে দাঁড়ালাম যাতে আলগোছে পকেটের মধ্যে পেতে দেওয়া যায়। একটুও ভাঁজ না পড়ে। খামটিকে পকেটের মাঝে পুরে, একটু আলতো ভাবে হাত বুলালাম ঠিকভাবে পাঁট করে রাখার জন্য। অনুভব করলাম খামটার মধ্যে কিছু একটা নরম দলা পাকানো বা কাগজ ভাঁজ করে ভরে দেয়া হয়েছে। একটা প্যাটার্ন হাতে অনুভূত হলো। ঈশরাত আপু নিশ্চয়ই আর একটি ডিজাইনের প্রজেক্ট করে লোকমান ভাইকে পাঠাচ্ছে। কিন্তু গোপনে কেন?
ভাবনাটাকে বাদ সাধলো ঈশরাত আপু।
বলল,
-‘যা, এখনই যা। তা না হলে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উনাকে হয়তো পাবি না।’
আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। চকিত আদেশ পেয়েই তাড়াতাড়ি রওনা হতেই ঈশরাত আপু হাত নেড়ে বলল,
-‘সাবধানে যাস। দৌড়ানোর দরকার নেই। সাধারণত যেভাবে হাঁটিস সেভাবে হাঁটবি। যাতে কেউ তোকে থামিয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করে, বুঝলি?’
আমি হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বড় রাস্তায় উঠে ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঈশরাত আপু ঠাই দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার খুঁটি ধরে। তাকিয়ে আছে আমার যাওয়ার দিকে। মনে মনে বললাম, ‘ঈশরাত আপু, আমি তোমার খামটা ঠিক লোকমান ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেব। চিন্তা কোরো না। কোন এদিক-ওদিক হবে না, দেখো।’
বুকটা আমার তখনও দুরুদুরু করছে। আমি কি দ্রুত হাঁটছি, না আস্তে হাঁটছি তা ঠাহর করতে পারলাম না। সাধারণভাবে হাঁটার গতি নির্দিষ্ট করা আমার জন্য বেশ দুষ্কর হয়ে উঠলো। আমি খুব সাবধানে লোকমান ভাইয়ের বাড়ির দিকে চললাম।
লোকমান ভাইয়ের বাড়ি যেতে গেলে বড় রাস্তা থেকে নেমে, পরে একটা সরু মাটির রাস্তা ধরতে হয়। রাস্তাটাকে এক পেয়ে পথ বলা যায়। পথের দু'ধারে বেশ বড় বড় ঘাস আগাছা জন্মেছে। রাস্তার উপর দিয়ে ভ্যান-রিক্সা বা যাতায়াতের ফলে তিনটে সমান্তরাল আর একটু সরু পথ হয়েছে। যেখানে চলাচলের ফলে ঘাস নেই। এই সরু তিনটে পথের মাঝখানের পথে আমি হাঁটতে লাগলাম। মিনিট কয়েক হাঁটার পর, পেছন থেকে সাইকেলের বেল দিতে শুনলাম সাইড দেওয়ার জন্যে। আমি বাম দিকের পথে সরে সাইড দেবো, না ডানদিকের পথে গিয়ে সাইড দেবো, বুঝতে না পেরে এক জায়গায় একটা খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। সাইকেলটি ফুস্ করে আমার বাঁ দিক দিয়ে আমাকে পার হয়ে চলে গেল।
এতক্ষণে বুঝলাম, আমি এপথ দিয়ে আগেও এসেছি, অনেক বারই এসেছি। আর আমি সাধারণভাবে হাঁটছি না। আমার উচিত ছিল, সবচেয়ে বাঁ দিকের পথ দিয়ে হাঁটা। সাইকেলওয়ালারা বাঁ দিক দিয়ে পেছন থেকে এলে, বেল বাজিয়ে বাঁয়ের পথ থেকে পথ পরিবর্তন করে মধ্যের পথ দিয়ে যাবে। এটাই নিয়ম। মনে হলো আমার মাথা পুরোপুরি কাজ করছে না। কোন ভুলভাল করে না ফেলি। কোনরকম ভুল করা চলবে না। তাহলে সর্বনাশ হবে। ঈশরাত আপু খুব আশাহত হবে। ভাববে আমি কোন কাজের না। একদম অকর্মার ঢেঁকী। তাছাড়া আমাকে এরকম একটা দায়িত্ব জীবনে আর কেউ কখনো দেয়নি। যদি ভুল করি তবে আর কোন দায়িত্বই হয়তো জীবনে কখনো পাবো না।
তারপর অতি সাধারণভাবে হেঁটে হাজির হলাম লোকমান ভাইদের বাড়ির সামনে। এতদিন এ পথ দিয়ে কতই যে হেঁটেছি, খেলে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ যেন নতুন করে দেখছি বাড়িটা। মনে হচ্ছে বাড়িটা একদম অচেনা। শুকনো কলা পাতা দিয়ে, বাঁশের চটা দিয়ে, বেড়া দেওয়া হয়েছে। রাস্তার থেকে যেন পুরোপুরি দেখা না যায়, তার জন্য। রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটলে বেড়ার ওপারে কি হচ্ছে খুব একটা বোঝা যায় না, দেখা যায় না। যদি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পরখ করা হয়, তবেই দেখা সম্ভব একটু আধটু। আমি বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, বাড়ির ভেতরে ঢোকা মনে হয় ঠিক হবে না। বাড়ির ভিতরের উঠানে কাউকেই দেখলাম না। উঠানে শুধু একটা কুকুর শুয়ে বিশ্রাম করছিল বোধ হয়। কুকুরটা আমার গতিবিধি আর ইতস্ততা দেখে মুখ তুলল। আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলাম ভয়ে ভয়ে।
কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো শোয়া অবস্থাতেই, দাঁড়ালো না। ঘর থেকে লোকমান ভাই বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। আমাকে দেখতে পাননি মনে হয়। ততক্ষণে কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়েছে। আমারও বাড়ির ভিতরে ঢুকতে বেশ ভয় করছিল। এই কুকুরটির ভয়। কুকুর দেখলে আমার খুউব ভয় হয়। কুকুরে কামড়ালে একটা ভীষণ তেষ্টার রোগ হয়। শুনেছি দুই সপ্তাহ ধরে পেটের নাভির চারপাশ দিয়ে প্রতিদিন মোটা সূচের একটা করে ইনজেকশন দিতে হয়। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তারপর দেখলাম কুকুরটা একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার লোকমান ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। লোকমান ভাই রাস্তার দিকে এলেন।
বললেন,
‘কিরে ভয় পেয়েছিস?’
ভয়ে ভয়ে বললাম,
-‘হ্যাঁ, অল্প।’
আমাকে আশ্বস্ত করে লোকমান ভাই বললেন,
-‘ভয় নেই রে। আমি সাথে থাকলে টমী তোকে কিছু বলবে না। ওর নাম টমী।’
বলেই টমীর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলেন।
টমী আনন্দে লেজ নাড়ছে। মনে হচ্ছিল, বেশ মজা পেয়েছে আমাকে দেখে। সে আস্তে আস্তে খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার হাফপ্যান্টের ডান পকেটে মুখ ঘষতে লাগলো। খুব অবাক আর ভয়ে আমি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।
-‘তোর নাম দীপ্ত না?’ লোকমান ভাই জিজ্ঞেস করলেন।
-‘হ্যাঁ।’
-‘কিরে কিছু বলবি?’
-‘হ্যাঁ।’
-‘বল্’
-‘এখানে বলা যাবে না। আপনার একটা জিনিস আছে আমার কাছে। ঈশরাত আপু পাঠিয়েছে।’ বলেই ডান পকেটের উপরে হাত দিলাম।
-‘আচ্ছা। তুই বড় রাস্তার দিকে যা। ফিরতি পথের দিকে হাট। আমি আসছি।’
বলেই আঙ্গুল নির্দেশ করে যে দিক দিয়ে এসেছিলাম সে দিকটা দেখিয়ে দিলেন।
আমি ওদিকে হাঁটা শুরু করলাম। কয়েক মিনিট পরেই সাইকেলের আওয়াজ পেয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি লোকমান ভাই সাইকেল চেপে প্রায় আমার কাছে চলে এসেছেন। কাছে এসেই সাইকেল থেকে নেমে আমার সাথে সমান তালে হাঁটা শুরু করলেন লোকমান ভাই। আমি বাঁ পাশের পথ ধরে আর লোকমান ভাই মাঝের পথ ধরে সাইকেল ঠেলে ঠেলে আমার সাথে সাথে হাঁটছেন।
লোকমান ভাই জিজ্ঞেস করলেন,
-‘কিরে, কি জিনিস আছে তোর কাছে?’
আমি সামনে-পেছনে, বামে-ডানে একটু তাকিয়ে সাবধানে পকেট থেকে খামটা বের করে লোকমান ভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। বললাম,
-‘এই যে এটা। ঈশরাত আপু দিয়েছে আপনাকে দিতে।’
-‘ও আচ্ছা।’
বলেই আমার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে খামটি আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে, জিনসের প্যান্টের পেছনের পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন,
-‘তুই কি আমার সাইকেলে চড়ে ওদিকে যাবি?’
আমি মাথা নেড়ে বললাম,
-‘না, ঠিক আছে। আমি ফুটবল মাঠে যাব। এই তো বেশী দূরে না, হেটেই যেতে পারব।’
পকেট থেকে চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে যে নিষ্কৃতি পেয়েছি, এটাই অনেক। ভাগ্যিস কেউ দেখে ফেলেনি। অন্য কেউ টের পেলেই আমাকে প্রশ্ন করত। এমনকি টমীও টের পেয়েছে। সে ঠিক আমার ডান পকেটের কাছে নাক দিয়ে শুঁকে মুখ ঘষছিল। ও ঠিকই বুঝেছে। পশুপাখিরা অনেক বোঝে। সেদিন ঈশরাত আপু তার বিজ্ঞান বইয়ে কুকুর নিয়ে পড়ছিল আর আমাকে তরজমা করে শোনাচ্ছিল। ইউরোপ আমেরিকায় নাকি অন্ধ লোকেরা কুকুর নিয়ে চলাফেরা করে। ঐ কুকুরদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কুকুর তার অন্ধ মালিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটি কুকুরের ঘ্রাণশক্তি নাকি মানুষের তুলনায় দশ হাজার থেকে এক লক্ষ গুন বেশী তীব্র। টমী নিশ্চয়ই আগেও ঈশরাত আপুর চিঠি শুঁকেছে। তাই মনে হয় সে আমার সাথে উচ্চবাচ্য করলো না, বন্ধুর মতো আচরণ করলো। ভালো আর পছন্দের ঘ্রাণ নাকি কুকুরেরা নাকের ডান ছিদ্র দিয়ে শুঁকে। কুকুরেরা নাকি এক দেড় মাইল দূর থেকেও গন্ধ বুঝতে পারে।
মনে হল, ঈশরাত আপুর খামটা আমার রক্ষাকবচের মতো কাজ করেছে। এখন ভালোবালাই মতো ফুটবল মাঠে যেতে পারলেই বাঁচি।
লোকমান ভাই বললেন,
-‘আচ্ছা, সেটাই ভালো হবে।’
বলেই সাইকেল চালাতে শুরু করতে গিয়েও এক পা দিয়ে ভর করে সাইকেলের উপরেই বসে বললেন,
-‘এর পরেরবার এলে তোকে কদমা খাওয়াবো। নন্দ সাহার তৈরি মজাদার কদমা।’
আমি ‘আচ্ছা’ বলে ঘাড় নাড়লাম। লোকমান ভাই চোখের পলকে দ্রুতগতিতে বড় রাস্তার দিকে হুড়মুড় করে তার সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন, যেন তার ভীষণ তাড়া আছে।
এরপর থেকে নিয়ম করে প্রতি বুধবার স্কুলের ছুটির পর বাড়িতে এসে হাতমুখ ধুয়ে, খেয়ে, ফুটবল মাঠে খেলতে যাওয়ার আগে ঈশরাত আপুদের বাড়ী গিয়ে খামটা নিয়ে লোকমান ভাইকে পৌঁছে দিতাম। পিয়নের কাজটা আমার একদম পাকাপাকি হয়ে গেল।
দানাদার বা বাতাসা খেতে খেতে প্রতি সপ্তাহের খামটা লোকমান ভাইয়ের জিম্মায় পৌঁছে দেয়া একটি এক্সাইটিং কাজ বলে মনে হতো। টমীকে গিয়ে একটু আদর করা, তারপর কদমা খেতে খেতে ফুটবল মাঠে গিয়ে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার জন্য উপস্থিত হওয়া, একটা রুটিন হয়ে গেল।
এভাবে বেশ কয়মাস চলল। এক বুধবারে আমি পিয়নের ডিউটি করতে গিয়েছি ঈশরাত আপুদের বাড়িতে। বাড়িতে পা দিতেই একটু অন্যরকম মনে হলো। বাড়ির উঠানের থেকে বারান্দার সবকিছু বেশ পরিপাটি করে গোছানো। উঠানের উপর রোদে শুকানোর জন্য টাঙানো তারের উপর কোন ধোয়া জামাকাপড়, শুকনো বা ভেজা লুঙ্গি, শাড়ি বা কোন কিছুই ঝুলছে না। যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র পরিপাটি করে সাজানো। লোকজনের কথাবার্তায় বাড়িটা বেশ জমজমাট। রান্নাঘরে ঈশরাত আপুর মায়ের সাথে রান্নাবান্নাতে জোগাল দিচ্ছে ওপাড়ার আর এক মহিলা। বারান্দায় যেখানে বসে ঈশরাত আপু পড়াশোনা করে, সেখানে চারজন লোক ঈশরাত আপুর আব্বার সাথে বসে কথা বলছে। আমি ওদের বাড়ির গেটের বেকী বেড়া পার হতেই থেমে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর এক পাও এগোতে সাহস হলো না। আমাকে ঠিক ঈশরাত আপুর আব্বা দেখে ফেললেন। বললেন,
-‘কিরে দীপ্ত, কেমন আছিস?‘
আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম,
-‘ভালো আছি আঙ্কেল। ঈশরাত আপু বাড়িতে আছে?‘
বারান্দায় বসা সবাই একবার আমাকে পরখ করে দেখে নিল। মেহমানদের একজন অল্প বয়সী। লোকমান ভাইয়ের থেকে দু চার বছরের বড় হবে বোধ হয়। তার প্যান্ট শার্ট পরা। বাকি তিনজন পায়জামা পাঞ্জাবী পরা। একজনের মাথায় মকমলের খয়েরী রঙের টুপী পরা। মনে হচ্ছে লোকটা এইমাত্র কাশ্মীর থেকে ভেড়া চরানো ছেড়ে উঠে এসেছে। টেলিভিশনের একটা বিদেশি অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম, কাশ্মীরে ভেড়ার রাখালরা ওরকম টুপী পরে পাহাড়ি শীতের জায়গায় ভেড়া চরায়। ঈশরাত আপুর বাবাও বেশ একটা জম্পেশ, আর ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি পরে বসে কথা বলছিলেন।
ঈশরাত আপুর আব্বা বললেন,
-‘ঈশরাত আজকে একটু ব্যস্ত আছে। মেহমান এসেছে, কালকে আসিস্।’
-‘আচ্ছা’
বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ির থেকে বের হওয়ার জন্য হাঁটা শুরু করলাম। গুঞ্জন কানে এলো,
-‘ছওয়ালডা কিডা?‘
ঈশরাত আপুর আব্বার গলা শুনলাম,
‘‘আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে। মাঝে মাঝে ঈশরাতের কাছে পড়াশোনা দেখিয়ে নিতে আসে।‘
-‘ও আচ্ছা‘, বলল প্রশ্নকারী।
ভাবলাম, আমার কাছে কোন বইপত্র, খাতা নেই। তাহলে ঈশরাত আপুর বাবা ওটা বললেন, যদি আবার মেহমানরা আরো কিছু একটা জিজ্ঞেস করে বসে? তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করছি এমন সময় দেখলাম ঈশরাত আপু ওদের রাস্তার দিকের জানালা খুলে হাত ইশারা করে আস্তে আস্তে বলল,
-‘কাল আসিস, কেমন?‘
হাত নেড়ে, চোখ বুজে, মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝালো,
-‘আজ কিছু নেই পাঠানোর।‘
আমি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নেড়ে ফুটবল খেলার মাঠের দিকে রওনা হলাম।
লোকমান ভাইদের বাড়ির সরু রাস্তা পার হয়ে ফুটবল মাঠে যেতে হয়। সরু রাস্তা পার হওয়ার পূর্বেই মনে হলো যদিও আজকে কিছু দেওয়ার নেই, তথাপিও লোকমান ভাইকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। তা না হলে হয়তো সে আমার আশায় বসে থাকবে। অগত্যা বড় রাস্তা থেকে নেমে লোকমান ভাইদের বাড়িতে যাওয়ার সরু মাটির পথে হাঁটতে হাঁটতে লোকমান ভাইয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই টমী আস্তে আস্তে একটু কুঁই কুঁই করে ডেকে পাশে এসে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগলো। তারপর টমী কাছে এসে আমার হাঁটুতে, পকেটের কাছে শুঁকে নিরুৎসাহীর মতো দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ানো থামিয়ে, মাটিতে শুয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে লোকমান ভাই শার্টটা গায়ে চাপাতে চাপাতে তার সাইকেলটা ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে আমার কাছে এলো।
আমার দিকে ইশারা করে বলল,
-‘কই?’
-‘আজ কিছু নেই’
-‘নেই কেন? ওদের বাড়িতে যাস্ নি?’
-‘গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, একগাদা মেহমান এসেছে।’
লোকমান ভাই একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
-‘তাই?’
-‘হ্যাঁ। ঈশরাত আপু আগামীকাল আমাকে যেতে বলেছে।’
-‘ও আচ্ছা।’
বলেই কাগজে মোড়া কয়েকটা কদমা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চিন্তিত মনে সাইকেল চালিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে গেলেন। কদমাগুলো হাতে ধরে খাব, কি খাব না তা ভাবলাম কিছুক্ষণ। আমি তো আজ পিয়নের কাজটা পরিপূর্ণভাবে করিনি। তাহলে কদমাগুলি কি আমার নেওয়া ঠিক হয়েছে? না, ঠিক হয়নি মনে হয়। কিন্তু কিছু বোঝার বা বলার আগেই তো লোকমান ভাই দ্রুতগতিতে চলে গেলেন। আচ্ছা, আজ না হয় টমীর সাথে ভাগাভাগি করে খাই। কাল যদি লোকমান ভাই কদমা দিতে চান তাহলে না নিলেই হবে। একটা কদমা টমীর দিকে উঁচু করে ছুঁড়ে দিলাম। টমী ঠিক ক্যাচ ধরে মুখের মধ্যে নিয়ে চুপচুপ করে শব্দ করে চুষে চুষে তারপর মাটিতে ফেলে তা আবার চেটে চেটে খেতে লাগলো।
টমীকে বললাম,
-‘যাহ, কিরে তুই? কদমা কামড়ে খা।’
বলেই আমার একটা কদমা কামড়ে ওকে দেখালাম যে কিভাবে কামড় দিয়ে খেতে হয়। কিসের কি? টমী কিছু বুঝলো বলে মনে হলো না! সে একইভাবে মুখের মধ্যে নিয়ে চুষে আবার মাটিতে ফেলে দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলো।
ওখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার খেলতে যেতে দেরি হবে। আমাকে ফুটবল মাঠে যেতে হবে।
বললাম,
-‘টমী, তোকে আমি অন্যদিন শিখিয়ে দেবো কিভাবে কদমা কামড়ে খেতে হয়।’
টমী কি বুঝলো জানিনা, তবে আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে একবার একটু তাকিয়ে, আবার কদমা চাটতে লাগলো। আমি চলে গেলাম খেলার মাঠে।
পরদিন কথামতো আমি ঈশরাত আপুর বাড়িতে গেলাম। ঈশরাত আপুকে দেখে খুব বিধ্বস্ত মনে হল। কাল থেকে মনে হয় চুল আচড়ায়নি। চুলগুলো যেদিকে খুশী সেদিকে এলোমেলো হয়ে আছে। চোখ ফোলা ফোলা, জবা ফুলের মত টকটুকে লাল। মনে হয় কোন কারণে অনেক কান্নাকাটি করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার কি হয়েছে?’
-‘কিছু না।’ বলেই অন্যদিকে তাকালো।
তারপর বলল,
-‘তুই দাঁড়া।’
বলেই ঘরে গিয়ে কয়েকটা দানাদার মিষ্টি আর একটা খাম ওড়নার মধ্যে লুকিয়ে এনে, দানাদার গুলো আমার হাতে দিয়ে, খামটা আমার পকেটে পুরে দিল।
আর বলল,
-‘এখন যা, আমি একটু শুয়ে থাকবো।’
ওদিনকার খামটা অন্য দিনের তুলনায় বেশ ভারী আর মোটা বলে মনে হল। পকেটে যে কিছু আছে তা হাঁটতে গেলে বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল। লোকমান ভাইদের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই চোখে পড়ল সে টমীকে নিয়ে রাস্তায় হাটাহাটি করছেন। আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,
-‘কিরে কি খবর দীপ্ত? কেমন আছিস?’
মাথা নেড়ে বললাম,
-‘ভালো।’
বলেই পকেট থেকে খামটা বের করে লোকমান ভাইকে দিলাম। খামটা নিয়েই সে তার জিন্সের পকেটে ভরে নিল। অন্য পকেট থেকে একটা কাগজে মোড়া কয়েকটা কদমা আমার হাতে দিয়েই তার বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। টমী তখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। আমি একটা কদমা বের করে সেদিনের মতো উঁচু করে ছুঁড়ে দিলাম। টমী কদমাটাকে ক্যাচ ধরে লোকমান ভাইয়ের পিছু নিল। লোকমান ভাই ঘাড় ঘুরিয়ে টমীকে কদমা দেয়ার ব্যাপারটা দেখল। তারপর একটু মুচকি হেসে তার বাড়ির দিকে চলে গেল।
এরপর আমার পিয়ন-ডিউটি সপ্তাহে একদিন থেকে বেড়ে সপ্তাহে দু’দিন হয়ে গেল। খাম দিতে গেলেই প্রায়ই দেখতাম লোকমান ভাই টমীকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাকে আর খুঁজতে হতোনা। আজকাল তাকে বেশ পেরেশান লাগে। লোকমান ভাইয়ের ছোট রিমোটের মত একটা মোবাইল ফোন দিয়ে অনেক কথা বলতে দেখতাম। ফোনে কথা বলতে বলতে সে অকারণে এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক অযথা হাটাহাটি করত। ঈশরাত আপুর কোন মোবাইল ফোন ছিল না। লোকমান ভাই হয়তো চাকরি-বাকরি কিছু খুঁজছেন বা অন্য কোনো বিষয় থেকে থাকবে। ঈশরাত আপু আমার সাথে বসে তেমন আর গল্প করত না। সব সময় কি যেন চিন্তা করত, অন্যমনস্ক থাকতো। দেখেই বোঝা যেত যে সেও বড় কোন ধকলের মাঝে আছে।
এতদিনে আমি ঠিকই বুঝে গেছি যে, ঈশরাত আপুর সাথে লোকমান ভাইয়ের লাইন আছে। ওরা একে অন্যকে খুব পছন্দ করে ও খুব ভালোবাসে। ঈশরাত আপুর মনে হয় লোকমান ভাইয়ের সাথে বিয়ে হবে।
একদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরে আমি পড়তে বসেছি। বারান্দায় আমার মায়ের সাথে আমার বাবার কথাবার্তা শুনে আমার খুব কান খাড়া হলো।
মা বাবাকে বলল,
-‘শুনেছ, ও পাড়ার ঈশরাতের বিয়ে ঠিক হয়েছে।’
শুনেই আনন্দে আমার চোখ বড় বড় হয়ে কান আরো বেশী খাড়া হলো। লোকমান ভাইয়ের সাথে ঈশরাত আপুর বিয়ে, এটা তো ওরা দুজনের কেউই আমাকে বলেনি। লোকমান ভাইকে বলতে হবে যে আমি তার বিয়ের বরযাত্রী হবো। যদিও খুব কাছে কাছেই বিয়ে। লোকমান ভাইদের বাড়ি থেকে ঈশরাত আপুদের বাড়িতে যেতে হাঁটার দূরত্ব। তাতে কি? আমরা বাজি পোড়াতে পোড়াতে, নাচতে নাচতে আনন্দ করবো। অনেক মজা হবে। আর আমাকে না নিয়ে পারবেই না। আমি তো ওদের দুজনের কাছে একটা খুউব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। বাবা একটা বই নিয়ে নিবিষ্ট ভাবে কি যেন পড়ছিলেন।
বাবা বললেন,
-‘ও। তা কবে বিয়ে?’
-‘এ মাসের শেষ শুক্রবারে। ২৮ তারিখে।’
-‘তার মানে তো খুবই শীঘ্রই। আর মাত্র ১০ দিন বাদেই বিয়ে। তা কোথায় বিয়ে ঠিক হলো?’
-‘ফরিদপুরের কি একটা জায়গায়।’
বলেই মা কোন প্রশ্নের জন্য আর তর সইতে না পেরে বড়বড় করে পূর্ণ বৃত্তান্ত বলা শুরু করলো।
মা বলল,
-’ছেলেটা নাকি দেখতে বেশ ভালো। শিক্ষিত ও সরকারী চাকরী করে। বেতন মোটামুটি ভালো। তবে অনেক উপরি আছে।’
বলেই বেশ গদগদ হয়ে পড়ল। বুঝলাম বেতনের চেয়ে উপরিটাই মায়ের বেশী গুরুত্বপূর্ণ। উপরিটা যে কি জিনিস তা বুঝলাম না যদিও। আমার মাথায় তখন কিছুই ধরছে না। পড়াশোনার বইয়ের কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। বুঝতে বাকি রইল না যে, ঈশরাত আপুর সাথে যার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে মোটেই লোকমান ভাই নয়। অন্য কেউ। বিশাল সর্বনাশ হতে চলেছে। ঈশরাত আপুর ফরিদপুর নামে দূরে কোথাও বিয়ে হচ্ছে। ঈশরাত আপুর সাথে আর বসে বসে গল্প শোনা যাবেনা। লোকমান ভাইয়ের সাথে বিয়ে হলেও মাঝে মধ্যেই গিয়ে হাজির হওয়া যেত। গল্প শোনা যেত, অরিগামী শেখা যেত। তাছাড়া দানাদার, কদমার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যেত। সব ভণ্ডুল হবে। খুব খারাপ হবে।
বাবা জিজ্ঞেস করলেন,
-‘তো, পাত্র কি চাকরী করে?’
মা বলল,
-‘কানুর গু।’
বাবা অবাক হয়ে, একটু স্পষ্টভাবে, আগের চেয়ে একটু উঁচু স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলেন,
-‘কি চাকরি?
-‘কানুর গু। তাই শুনলাম।’
-‘কানুর গু?’
বলেই, বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসির তোড়ে তার হাত থেকে বইটা ফ্লোরে পড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম। বাবা হাসলে এরকম করেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হাসেন। একদম নির্ভেজাল সে হাসি। হাসছেন তো হাসছেনই, আর চেয়ারের হাতল চাপড়াচ্ছেন। কোনভাবেই হাসি ঠেকাতে পারছেন না। তাই চেয়ারের হাতল চাপড়িয়ে নিজেকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছেন। আমরা সবাই হা করে চুপ করে বসে আছি। এর মধ্যে মা যেন কি বলেছিল। কিন্তু বাবার হাসির তোড়ে তা আর আমি শুনতেই পাইনি।
আমারও একটু খটকা লাগলো। মা কানুর কথা বলছে কেন? আমাদের ও পাড়ায় কানুগোপাল নামে একজন লোক আছে। খুব খচ্চর আর কেউটে ধরনের লোক। মাঝে মাঝেই বাচ্চাদেরকে অযথা ভয় দেখায়। একদিন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছি। হঠাৎ করে নিঃশব্দে সাইকেল নিয়ে, বলা নেই কওয়া নেই আমার কাছাকাছি পেছনে এসেই ঘেউ ঘেউ করে একদম কুকুরের মত ডাক দিয়ে ফুস্ করে বেরিয়ে গেল। আজব। আর একটু হলেই আমি ভয় পেয়ে, রাস্তার পাশে পড়ে যেতাম কুকুরের ভয়ে। সবাই কানুগোপালকে সংক্ষেপে “কানু” বলে ডাকে।
কিন্তু কানুর মতো একটা খচ্চর লোকের গু পরিষ্কার করতে কোন সরকারী লোকের কেন দরকার হবে? তাও আবার ফরিদপুরের লোক। কে জানে? ওই কানু হয়তো যেখানে সেখানে রাস্তাঘাটে পায়খানা করে রাখে। বাবার হাসি থামলে তারপর বললেন,
-‘আরে কানুর গু না। কানুন গো।’
-‘কি জানি বাবা। ঈশরাতের আম্মা তো তাই কইলো।‘
বাবা বললেন,
-‘কানুনগো একটা সরকারী পদ। হ্যাঁ, খারাপ না।‘
-‘কানুনগোদের কি কাজ?‘
-‘জমিজমার সার্ভে, মানে মাপঝোপ করে কানুনগো পদের চাকরী করা লোকজন।’
-‘তার মানে কি সরকারী আমিন?’
-‘তা ঠিক না, তবে কাছাকাছি।
-‘তাহলি ঠিক আছে। জমিজমা মাপতি যাইয়ে এট্টু আট্টু কম বেশি দিলিই তো পয়সা। মাইয়েডা ভালোই থাইকপেনে।’
এবার উপরির ব্যাপারটা বুঝলাম। আর মা যে সেটার খুব গুরুত্ব দিচ্ছে তাও বুঝলাম।
লোকমান ভাইয়ের জন্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তখনই গিয়ে লোকমান ভাইকে এ খবরটা দিয়ে আসি। কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার হয়েছে। এ অন্ধকারে কোনভাবেই আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না। মনস্থির করলাম যে, কাল সকালে স্কুলে যাওয়ার আগেই লোকমান ভাইকে খবরটা জানাতে হবে। কিন্তু তারপর লোকমান ভাই কি ব্যবস্থা নেবে? ঈশরাত আপুর হবু বর তো একটা ভালো সরকারি চাকরী করে। আর লোকমান ভাই তো বিএ পাস করে মাত্র চাকরী খুঁজছে। কবে চাকরী পাবে তা কি কেউ জানে?
দেখতে দেখতে মাসের শেষ ঘনিয়ে এলো। ঈশরাত আপুদের বাড়ি রঙিন কাগজ তিন কোনা করে কেটে, আঠা দিয়ে সুঁতুলির সাথে লাগিয়ে লম্বা লম্বা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। উঠোনে বড়ো চাঁদোয়া খাঁটিয়ে প্যান্ডেলের মতো করা হয়েছে। বিরাট জমজমাট ব্যবস্থা।
ঈশরাত আপুর বিয়ে হয়ে গেল কানুন গো জামাইয়ের সাথে। বিয়ে অনুষ্ঠানমালার অনেক অংশেই আমি উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের সাজে ঈশরাত আপুকে যে কি দারুণ সুন্দর লাগছিল, সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। লাল একটি শাড়ীর মাঝে অনেক সোনালী রঙের কাজ করা। শাড়ীর পাড়টাকে মনে হচ্ছিল স্বর্ণ দিয়ে বানানো। নাকে নথ, মাথায় টিকলি, বড় আর ভারি হার, চুড়ি, হাতে মেহেদীতে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ডানা কাটা পরী। যেন এখনই তার পীঠে হাল্কা গোলাপি দুটো পাখা গজিয়ে উড়ে চলে যাবে গাছের উপর দিয়ে আকাশে।
বিয়ে হয়ে গেল বটে, কিন্তু পুরো সময়টাতেই ঈশরাত আপু মুখ খুব গোমড়া করে বসে ছিল। ভিডিওম্যান ও ক্যামেরাম্যানদের অনেক অনুরোধেও হাসতে পারল না। শুধু সবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল, যেন সে কাউকে দেখতেই পাচ্ছে না। আমাকে এক সময় হাতের ইশারা করে কাছে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল একটু পরে আমি একা হলে আমার সাথে দেখা করিস্। আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ সম্মতি দিলাম। আমি তাকে তাকে থাকলাম, কখন ঈশরাত আপু একটু একাকী হয়। এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। ঈশরাত আপু আজ ওখানকার মধ্যমণি। একাকী পাওয়া? সে যে বিরাট দুষ্কর ব্যাপার। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। লোকজন, আমন্ত্রিত অতিথিরা, পাড়াপড়শী সবাই আসছে বউ জামাই দেখতে। সে এক লোকে লোকারণ্য অবস্থা।
সবাই যখন বিকেলের চা নাস্তা খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমি কয়েক মিনিটের জন্য ঈশরাত আপুকে একাকী পেলাম। ঈশরাত আপু তার মাথার চুলের সাথে বাঁধা, কপালের উপর ঝুলে থাকা সুন্দর টিকলিটা খুলে, বিছানার নিচ থেকে একটা কাগজ বের করল। কাগজের চারভাঁজের মধ্যে টিকলিটা ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে দিল।
বলল,
-‘দীপ্ত এটা ওকে দিস।’
বলেই সে হাউমাউ করে ফুপিয়ে কেঁদে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।
আমি কি করবো বুঝতে পারলাম না। ঈশরাত আপুকে কি সান্ত্বনা দিয়ে, না কাঁদতে অনুরোধ করব? নাকি চলে যাব? ভেবে পেলাম না। কয়েকজন হাসাহাসি করতে করতে ওই রুমের দিকে আসছে শুনেই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। আমার মাথায় বুদ্ধি খেললো যে এখানে একা ঘরে কেনই বা দাঁড়িয়ে আছি? কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে। ঈশরাত আপুকে কান্নারত রেখেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।
উঠানে বসা-দাঁড়ানো মেহমানরা, অন্যান্য দর্শনার্থীরা গুঞ্জন করছিল যে চা-নাস্তার পরপরই জামাই-বউ রওনা হবে। এই অধ্যায়টা আমি এ এলাকার বিয়েতে বারবার দেখেছি। বউ শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় অনেক কাঁদে। সে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর, বিভিন্ন শব্দের কান্না। আর নতুন বউ কাঁদবেই বা না কেন? জন্মের পর থেকেই যে মেয়ে তার আশেপাশের প্রিয়জনের সাথে ছিল, সে এখন ছেড়ে চলে যাচ্ছে একটা অজানায়। যে জায়গা, মানুষজন, পারিপার্শ্বিকতা, সবকিছুই তার কাছে অপরিচিত। তারপর চিন্তা থাকে, সেখানে সবাই তাকে এই চির চেনা সবার মত স্নেহ করবে, ভালবাসবে তো? তার সব অভ্যাস পাল্টে ফেলতে হবে, তার সব শখ হয়তো হারিয়ে যাবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দামই থাকবে না। ইচ্ছে হলেও সে তার প্রিয়জনগুলোর সাথে দেখা করা, কথা বলা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হতে পারবে না। বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন হয়তো অন্য কোন নামে তাকে ডাকবে। বাবা-মায়ের দেয়া এই অতি আদরের সাধারণ কিন্তু অমূল্য নামটাও হয়তো পাল্টে ফেলতে হবে। কে জানে? হয়তো এত সাধারণ নামে বর্তমানে বা পূর্বে শ্বশুরবাড়িতে কোন কাজের মেয়ে ছিল কোন এক কালে। সবই সম্ভব।
কান্না একটা সংক্রামক ব্যাপার। আশেপাশে অন্য কাউকে কাঁদতে দেখলে তার পাশের মানুষজনের কান্না পায়। কান্না না পেলেও তার মন বেশ খারাপ হয়ে যায়। ভাবলাম, কান্না পাক, আর যাই হোক, প্রিয় ঈশরাত আপুর বিদায় দৃশ্যতে আমি সাথে থাকবো। তাতে নিঝোরে কান্না পেলে কাঁদবো। মন থেকে যদি অনেক কান্না পায়, সে কান্না যদি বুকের খুব ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, তবে সে কান্নাকে আটকে রেখে লাভ কি? আমার আপন জনের জন্য কাঁদবো, তাতে কার কি বলার আছে বলো?
হাত দিয়ে পকেটে রাখা কাগজে মোড়া টিকলিটাকে একটু ছুঁয়ে নিলাম, যে ঠিকঠাক আছে কিনা। মেহমানরা সবাই রঙিন চাঁদোয়ার নীচে গোল হয়ে বসে নাস্তা খাওয়া সেরে, জম্পেশ করে চা খাচ্ছে। সবাই একে অন্যের সাথে কথা বলছে। আমরা ছোটরাও নাস্তা খেয়ে দৌড়াদৌড়ি, লাফ-ঝাপ, খেলাধুলায় ব্যস্ত। ওপাশে পাড়ার বউরা ঘোমটা মাথায় উঁকি দিয়ে নতুন জামাইকে দেখার পর নিজেদের মধ্যে হাল্কা কথাবার্তা, মাঝেমাঝে হাসি-খুনসুটি করছে। সব মিলিয়ে গুমগুম শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বড় রঙিন চাঁদোয়ার নীচেটা।
হঠাৎ ঈশরাত আপুর ঘরের বারান্দা থেকে বরপক্ষের একজন মেয়ে একজন মহিলাকে ডেকে বলল,
-‘আমি বউকে সাজগোজ ঠিক করে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার জন্যে সাহায্য করছিলাম। বউয়ের টিকলিটা পাওয়া যাচ্ছে না।’
মহিলাটা হতভম্ব হয়ে বিস্ময়ের সাথে বলল,
-‘বলিস কি? ওটা তো স্বর্ণের টিকলি। ইমিটেশনের না। সবখানে খুঁজেছিস্?’
বলেই তড়িঘড়ি করে ঈশরাত আপুর ঘরে গেল। আমি খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে চুপ হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালাম।
ঘরের ভিতরে মহিলাটা ঈশরাত আপুকে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল,
-‘টিকলি কি খুলেছিলে, কোন কারণে?’
ঈশরাত আপু বলল,
-‘না।’
-‘তাহলে গেল কোথায়?’
-‘তা জানি না। হয়তো কোথাও পড়ে গিয়েছে।’
-‘টিকলিটা পড়লে তো এই খাটের উপরে বা আশেপাশেই পড়বে।’
ঈশরাত আপুকে কিছু বলতে শুনলাম না। চার-পাঁচ জন মহিলা আর মেয়ে মিলে ঘরের দরজার চৌকাঠ থেকে শুরু করে প্রতিটি কোনা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো।
বর পক্ষের একজন অতি উৎসাহী মেয়ে উঠানে এসে বরপক্ষের মাতব্বর শ্রেণীর একজনের কানে কানে কি যেন বলে গেল। কানে কানের কথা ওই গোল মিটিঙের এক এক করে সবার কানেই গেল। সবাই একটু রাগান্বিত আর বিরক্ত মুখে একে অন্যের মুখের দিকে তাকালো।
তাদের একজন মিনমিন করে বলল,
-‘এইরহম আগেও দেখিছি। সুনার জিনিস দেখাইয়ে, রুপোর জিনিস দেয়। আর এতো দিন-দুপুরী ডাহাতি। এক্কেবারে পুইরোডাই গায়েফ!’
এই “গায়েফ” কথাটা শোনার সাথে সাথেই আমার গা চমকে উঠলো। আমার পকেটেই তো আছে গায়েব হওয়া টিকলিটা। এখনই হয়তো তুলকালাম কিছু একটা বেঁধে যাবে। চোর ধরার জন্যে হয়তো সবাইকে তল্লাশি করবে, কিংবা বাটি চালান দেবে। কে জানে? আমাকে হয়তো চোর সাব্যস্ত করে গণধোলাই দেবে। বাড়িতে ঢোকার বেকী বেড়ার দিকে যে ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ খেলছিল, আমি আস্তে আস্তে তাদের ওখানে গেলাম, যেন ওদের সাথে খেলতে যাচ্ছি। একটুখানি খেলার পরে আমি ওদেরকে বললাম যে আমার বাড়ি যেতে হবে। বলেই টুক্ করে, টু শব্দ না করে, বেরিয়ে এলাম।
ঈশরাত আপুর বিদায় দৃশ্য আমি দেখতে পাইনি। তার কষ্টের গভীরতা যদিও আমি ঠিক ঠিক কল্পনা করতে পারি। আমি আর দেরী না করে সোজা লোকমান ভাইয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পকেটের মাঝে টিকলিটা আছে কিনা, বার বার পকেটে হাত দিয়ে পরখ করে নিচ্ছিলাম। বড় রাস্তা থেকে নেমে লোকমান ভাইদের বাড়িতে যেতে সরু মাটির রাস্তা ধরে আসার সময় কাউকেই চোখে পড়লো না এই বিকেলের শুরুতে। এদিককার অনেককেই বিয়ে বাড়িতে দেখেছি। লোকমান ভাইদের বাড়ির সামনে আসতেই টমী কুঁইকুঁই করে কাছে এসেই লেজ নেড়ে নেড়ে আমার যে পকেটে টিকলি মোড়ানো কাগজটা আছে সেখানে মুখ ঘষতে লাগলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু লোকমান ভাই বেরিয়ে এলো না। সে বাড়িতে আছে কিনা কে জানে?
আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম,
-‘লোকমান ভাই, বাড়িতে আছেন?’
লোকমান ভাইয়ের মা রান্নাঘর থেকে একটু মুখ বের করে বললেন,
-‘লোকমান বাড়িতে নেই। সাইকেল নিয়ে বাজারে না কোথায় যেন গেল।‘
-‘আচ্ছা। বাড়ি আসলে বলবেন যে আমি এসেছিলাম দেখা করতে।’
-‘বলবা নে।’
বলেই তিনি তার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।
আমি তখন কি করি? বাড়ি যাবো, না ফুটবল মাঠে যাব? ভেবে স্থির করতে চিন্তা করছি। মনে হলো, নাহ্ ফুটবল মাঠে যাওয়া যাবে না। দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে টিকলিটা খেলার মাঠে পড়ে হারিয়ে গেলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত নিলাম, লোকমান ভাইদের বাড়ির রাস্তা দেখা যায় এমন কোথাও তার জন্য অপেক্ষা করবো। অগত্যা ওনাদের বাড়ির কাছেই মাঠের মধ্যে একটা কচাগাছ তলায় গিয়ে হাজির হলাম। কয়েকটা খণ্ড জমি পার হলেই কচা গাছটা। বেশ বড়সড় সাইজের গাছ। গাছের তলায় বেশ পরিষ্কার। হয়তো আশেপাশের কৃষকরা কাজের ফাঁকে এখানে একটু বিশ্রাম করে কচাগাছের ছায়ায়। এখান থেকে লোকমান ভাইয়ের বাড়িতে ঢোকার রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। চেয়ে রইলাম পথের দিকে কখন লোকমান ভাই বাড়িতে ফিরবে।
সে অনেকক্ষণ হবে বোধ হয়। কি করব ভেবে না পেয়ে পকেট থেকে সেই টিকলি টা বের করলাম। কি সুন্দর অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটা ডিজাইন! চাঁদের দুই কোনা থেকে দুটি, আর মাঝখান থেকে একটি চেইনের টানা দিয়ে একত্রিত হয়েছে একটু উপরে গিয়ে। অর্ধচন্দ্র থেকে সাতটি ছোট ছোট বলের ঝুলুম ঝুলছে। মাঝের ঝুলুমটা একটু বেশী লম্বা করে ঝুলে আছে, অন্যান্য ঝুলুমগুলোর চেয়ে। টিকলির লকেটটা একটা বেশ চওড়া চেইনের সাথে ঝুলছে। চেইনের অন্য মাথায় একটা হুকের মতো, দেখতে অনেকটা বড়শীর মতো আংটা। যা দিয়ে চুলের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়েছিলো। টিকলিটা পরার পর ঈশরাত আপুকে খুব সুন্দর মানিয়েছিল। টিকলিটা কাগজের মধ্যে ফের রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল ওই কাগজটা। কাগজটাতে কি যেন গোটা গোটা করে লেখা। ঈশরাত আপুর হাতের লেখা। লেখাটা অনেকবার পড়লাম। অনেকবার। এভাবে বারবার পড়াতে চিঠিটা আমার এক্কেবারে মুখস্থ হয়ে গেলো। তাতে লেখা ছিল,
“প্রিয়তম টমীর বাবা,
আমি মরে গিয়েও বেঁচে থাকব।
তুমিও মরে বেঁচে থেকো।
এই টিকলিটা তোমাকে দিলাম।
জেনো, আমার যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।
তুমি বেঁচে থাকলে অন্তত চোখের দেখাটা দেখতে পাবো।
ইতি,
-শুধু তোমার টিকলি।”
আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, ঈশরাত আপু লোকমান ভাইকে আদর করে “টমীর বাবা” বলে ডাকে। আর লোকমান ভাই ঈশরাত আপুকে আদর করে ডাকেন “টিকলি” বলে। ওগুলো আসলে ওদের একে অন্যকে দেয়া গোপন নাম।
চিঠির একদম শেষে লাল রঙের একটা লিপস্টিকের ঠোঁটের মত আঁকা। তবে এই লাল রঙের ওখানে বেশ একটা সুন্দর ঘ্রাণ আছে। এই মাঠের ফুরফুরে বাতাসেও ঘ্রাণটা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করলাম যাতে ঘ্রাণটা বাতাসে আর উড়ে না যায়। কাগজের মধ্যে যত্ন করে টিকলিটা ভরে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম, যেন আপাচাপ কেউ এসে পড়লে দেখতে না পায়।
এক সময় দেখলাম লোকমান ভাই খড়্খড়্ করে সাইকেলের শব্দ করে যেন পাখির মত উড়ে এলো ওনাদের বাড়ির ওখানে। সাইকেলের গতি না কমিয়েই সাই করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি করে আমি লোকমান ভাইদের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। মাঠের আইলের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম বটে, কিন্তু আমার চোখ ওনাদের রাস্তার দিকে। কি জানি, যদি আবার কোথাও কোন কাজে বেরিয়ে যায় তাহলে একটা ভারী সমস্যা হবে।
লোকমান ভাইয়ের বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই টমী এসে আবার লেজ নাড়তে লাগলো। আর আমার পকেটের কাছে মুখ ঘষতে লাগলো। লোকমান ভাই এলো না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওনার মা নিশ্চয়ই এখনো আমার খবরটা দেয়নি বা দেওয়ার সময় পায়নি। এদিকে আমারও খেলার সময় প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে।
আস্তে আস্তে লোকমান ভাইকে ডাকলাম,
-‘লোকমান ভাই।’
-‘কে?’
-‘আমি।’ বলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম টমীর সাথে।
লোকমান ভাই বাইরে থেকে এসে মনে হয় হাত মুখ ধুচ্ছিল। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রাস্তার দিকে এলো। পরনে একটা জিন্সের প্যান্ট, আর তার গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। চুলগুলো লম্বা উল্লোঘুল্লো। ঝাঁকড়া চুলে বাতাস লেগে ফুরফুরিয়ে উড়ছে, যেন কোন যত্ন পড়েনি কয়েকদিন।
বলল,
-‘কিরে দীপ্ত, তুই এখানে?’
চোখে তার আশ্চর্য হওয়া দেখে মনে হল সে আমাকে আজ এ সময়ে আশা করেনি।
বললাম,
-‘ঈশরাত আপু এটা দিয়েছে আপনাকে দেয়ার জন্য।’
বলেই কাগজে মোড়া টিকলিটা হাত উঁচু করে সামনে এগিয়ে ধরলাম। লোকমান ভাই কিঞ্চিত দ্বিধার সাথে কাগজটা হাতে নিলেন। টমী লেজ নাড়তে নাড়তে মুখ উঁচু করে লোকমান ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো। কাগজের মধ্যে টিকলিটার একটু কড়কড় শব্দ হতেই টমী দুবার ফুঃ ফুঃ করে ডেকে উঠলো। লোকমান ভাই কাগজে মোড়া টিকলিটা জিন্সের পকেটের রেখে বললেন,
-‘একটু দাঁড়া, আমি আসছি।’
বলেই বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। লোকমান ভাই ফিরে এলেন অন্য দিনের চেয়ে অনেকটা বড়, সাদা প্যাকেট নিয়ে। কাছে এসে আমার হাতে প্যাকেটটা দিয়ে বললেন,
-‘নে খাস্।’
অবাক হয়ে আমি বললাম,
-‘তাই বলে এতগুলি কদমা?’
-‘হ্যাঁ। তোর জন্য কিনে এনে ঘরে রেখেছিলাম, অল্প অল্প করে দেবো বলে। এখন থেকে আর লাগবেনা তোর কদমা, তুই নিয়ে যা।’
প্যাকেট থেকে দুটো কদমা টমীর দিকে উঁচু করে একটা একটা করে ছুঁড়ে দিলাম। টমী প্রথমটা ক্যাচ ধরল। দ্বিতীয়টা শূন্যে ছোড়ার সাথে সাথে প্রথম কদমাটাকে মুখ থেকে মাটিতে রেখে, দ্বিতীয়টা ক্যাচ ধরে মুখে রাখল। তারপর অপলকে মাটিতে রাখা প্রথম কদমার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। আমিও কদমার প্যাকেটটা নিয়ে ফুটবল মাঠে খেলতে চলে গেলাম। আমার মনে আছে আমি সেদিন সব ফুটবল-বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে কদমাগুলি খেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আজ আমার পিয়নের চাকরী থেকে এটা যেন বিদায় সম্বর্ধনা।
জানো, এর পরের ব্যাপারগুলো ঘটলো খুব তাড়াতাড়ি, ঝড়ের গতিতে। আমি সব খবর পেতে লাগলাম আমার মায়ের সাথে গল্প করতে আসা এক মুখরা পড়শির গল্প গুজব থেকে। এখানকার মহিলারা দুপুরের খাওয়া পরবর্তী বাসন-কোসন মাজা, সবকিছু গুছিয়ে রাখা, এসব কাজ সেরে এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে একটু গল্প-গুজব করে। গল্প-গুজবের অধিকাংশ বিষয়ই কোন না কোন সমালোচনা, কুকথা ভরা। আমার মা অবশ্য ভালো শ্রোতা। এ সময়টা আমারও তেমন কিছু করার থাকতো না। স্কুল থেকে এসে তাই মুখরা পড়শি এলেই কান খাড়া করে থাকতাম। যা শুনলাম, ঈশরাত আপুর বিয়ের পরদিন ভোরে লোকমান ভাই নাকি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। সে তার সাইকেলটা নিয়ে গিয়েছে। কে না কে দেখেছে যে, সে এখান থেকে বেশ দূরে জেলা শহরের পাশের একটা বড় হাইওয়ের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কোথায় যাচ্ছে। শুনে খুব ভয় পেলাম, যদি বাস বা ট্রাকে ধাক্কা দেয়।
মাস খানেক পর একদিন শুনলাম, লোকমান ভাই বাড়িতে ফিরে এসেছে তার অজ্ঞাতবাসের পর। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়ে, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করে, কঙ্কালসার হয়ে ফিরেছে। তার মুখের চোয়াল বসে গিয়েছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি থাকলেও নাকি বোঝা যায় যে তার মুখে মাংস বলতে কিছু নেই। দেখে নাকি তাকে আর চিনতে পারা যায় না। তার ঘাড়ে নাকি “টিকলি” নামে একটা জ্বীন-পরী আছর করেছে। ঝাড়-ফুঁক করার জন্য লোকমান ভাইয়ের আব্বা একটা ফকির এনেছিলেন। লোকমান ভাই তাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন নাকি দিনের অনেক সময়ই ওদের বাড়ির কাছের বড় কচাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে লোকমান ভাই অভিনয় করে, আর বক্তৃতা দেয়। লোকমান ভাই ফিরে এসেছে বটে কিন্তু সাথে এনেছে একটা কাগজের তৈরি বল। বড় সাইজের ফুটবলের মত কাগজের বল। সে সবসময়ই নাকি ওই বলটা বগলদাবা করে গোলকিপাররা ফুটবল ধরে যেভাবে ফুটবল খেলার মাঠে খেলতে নামে, সেরকম ধরে ঘোরাফেরা করে। ঘাড় থেকে জ্বীন-পরী নামানোর ঝাড়ফুঁকের ফকির নাকি তাড়া খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বলেছিল, ‘জ্বীন-পরী ওই বলের মইধ্যেখানে বইসে আছে।’
এলাকার সবারও একই ধারনা। ফকির ফর্দ দিয়েছে যে, বলটাকে একটি মাটির নতুন হাড়ির মধ্যে ভরে, এগারটি জ্যান্ত তেলো টাকি মাছের মাথা কেটে ঐ হাড়ির মধ্যে রাখতে হবে। তারপর হাড়ি মাটির সরা দিয়ে ঢেকে, পিচ গলিয়ে হাড়ির মুখের ফাঁকফোকর ভালভাবে বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে। তবেই নাকি লোকমান ভাইয়ের ঘাড়ে ভর করা জ্বীন-পরী তাকে ছেড়ে যাবে। লোকমান ভাইয়ের বাড়ির সবাই তাকে তাকে আছে, ফকিরের ফর্দ পালন করার অপেক্ষায়। সুযোগ পেলেই ফকিরের ফর্দ অনুযায়ী বলটাকে হাড়িতে ভরে ওভাবে নদীতে ভাসিয়ে চালান করে দেবে।
ভাবলাম, একদিন দিনের বেলায় ওই কচাগাছ তলায় গিয়ে লোকমান ভাইকে দেখে আসব। কিন্তু চিন্তাটা মাথায় আসতেই বেশ ভয় ভয় করল। আবার মনে হলো, কিছু একটা ফ্যাকরা আছে। স্থির করলাম, আমাদের পাড়ার কোন বন্ধুকে নিয়ে যাব। তাতে একটু সাহস পাওয়া যাবে।
ভয়ের একটা বড় কারণ হলো লোকমান ভাই একটা ধারালো ছুরি নিয়ে নাকি তাড়া করে। সেটা অবশ্যই ভয়ঙ্কর বৈকি? এইতো সেদিনই নাকি তার সর্বক্ষণের সাথী ওই ধামা সাইজের কাগজের তৈরি বলটা কয়েকটা বখাটে দুষ্টু ছেলেরা ছিনিয়ে নিয়ে প্রথমে ক্যাচ-থ্রো খেলেছিল। লোকমান ভাইয়ের মাথার উপর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলেছিল। লোকমান ভাই নাকি অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল কাগজের বলটি ফেরত দেওয়ার জন্য। কিন্তু বখাটে দুষ্টু ছেলেরা সেটি ফেরত দেয়নি। তারপর ওই দুষ্টু ছেলেদের একজন কাগজের বলটিকে গোলকিপারের মতো প্রথমে জোরে শটলাথি দিয়ে দূরে দিলো। হাসাহাসি, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ফুটবলের মত লাথি দিয়ে খেলা শুরু করল, তখন লোকমান ভাই আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারেনি। যে সব লোকজন গোল হয়ে ঘিরে তামাশা দেখছিল, তাদের মধ্যের একজন ডাব বিক্রেতার কাছ থেকে দা ছিনিয়ে নিয়ে, দা উঁচু করে মহা উন্মাদের মত একটা ঘূর্ণি দিয়ে
-“কুপাইয়ে ফালা ফালা করে ফেলবো”
বলে হুংকার দিলে সবাই জান বাঁচিয়ে পালিয়েছিলো।
সবাই পালালে লোকমান ভাই তার কাগজের বলটা বুকে জড়িয়ে ধরে নাকি রাস্তার উপর বসে চিৎকার করে অনেক কেঁদেছিল আর বিড়বিড় করে অনেককিছু বলেছিল। সেই থেকে লোকমান ভাই সব সময় একটা ধারালো ছুরি নিয়ে ঘোরে। তবে কাউকে কখনো সেটা দিয়ে খোঁচা টোঁচা দিয়েছে বলে শোনা যায়নি। ছোটখাটো দাঁ ছুরি নিয়ে যে কেউ তো ঘুরতেই পারে। এটাতো কোন মহা অপরাধ না, কি বলো? লোকমান ভাই কারো ক্ষতি করে না। সে থাকে তার মত। তবে তার নিজস্ব কিছু সম্পদ রক্ষা করতে যদি হিংস্র হতে হয় তাতে কি তার কোন দোষ আছে? এরপর থেকে কোন বখাটে দুষ্টু ছেলেরা বা কেউই এই টিকলি-পরীতে আছর করা লোকমান ভাইয়ের কাছ থেকে কাগজের বলটি ছিনিয়ে নিতে সাহস করেনি।
একটা ছুটির দিনে আমি আর এ পাড়ার ফুটবল-বন্ধুকে নিয়ে লোকমান ভাইদের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। বন্ধুটি যদিও প্রথমে রাজী হয়নি।
কিন্তু বলল,
-‘যাতি পারি। তয় লইক্ক্যা পাগোল দাবোড় দিলি কিন্তু আমি ঝাইড়ে দোইড় মারবানে।’
ইদানীং লোকমান ভাইকে এ এলাকার লোকজন “লইক্ক্যা পাগোল” বলে ডাকে।
বললাম,
-‘আচ্ছা। তুই দোইড় মাল্লি আমি কি আর বইসে থাকপানে নাকি? চল যাই, দেখি কি হয়।’
বুকের মাঝে দুরুদুরু করছে ভয়ে। লোকমান ভাইদের বাড়ি যত কাছে আসছে ততই বুকের সেই দুরুদুরুটা বাড়ছে। লোকমান ভাইদের বাড়ির সামনে এসে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে পাঁচিলের বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারলাম। কিন্তু বাড়িতে কাউকে দেখতে পেলাম না। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে ইতস্তত কাটল আমাদের। তারপর হঠাৎ টমীর ডাক শুনেই চকিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজলাম তাকে। আবার সে ফুঃ ফুঃ ডাক দিল। বুঝলাম সেই শব্দটা কচাগাছের ওদিক থেকেই আসছে। তাকিয়ে দেখি টমী কচাগাছের নীচে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ভয়ে ভয়ে মাঠের আইলের উপর দিয়ে টমীর দিকে আগাতেই চোখে পড়লো লোকমান ভাই মাটিতে বসে আছে মাথা নিচু করে।
আস্তে আস্তে আমরা প্রায় লোকমান ভাইয়ের কাছাকাছি আসতেই সে উঠে দাঁড়ালো। আমি আরো কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু আমার বন্ধুটা ভয়ে আইলের উপরে ঠাই দাঁড়িয়ে থাকলো। মনে হয় ভয়ে তার পা আর চলছিলো না। লোকমান ভাই ছুরি উঁচু করে আমার বন্ধুটিকে ইশারা করে বলল দূরে যেতে। বন্ধুটি আরও একটু পিছু হঠে বিপদমুক্ত দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি কচাগাছ তলায় এলাম বটে, কিন্তু বেশ খানিক দূরত্ব রেখে মাটিতে চুপটি করে বসলাম। লোকমান ভাই তার ছুরিটি কোমরে গুঁজে রেখে আমার দিকে খুব মন খারাপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আগের স্থানে মাটিতে বসে পড়ল। আমার ভয় করলেও, আমি জানতাম লোকমান ভাই আমাকে কিচ্ছু বলবে না। আপন বুঝ তো পাগলেরও আছে।
তার সামনে অনেক কাগজ। আজ তেমন বাতাস নেই এই ভর দুপুরে। তার পরেও লোকমান ভাই প্রতিটি কাগজের উপর একটা করে ছোট ঢেলা দিয়ে ভারা দিয়ে রেখেছে, যেন বাতাসে কোন কাগজ উড়ে না যায়। ছড়ানো সব কাগজ ভর্তি অনেক কিছু লেখা। পাশে কয়টা খামও আছে। খামগুলি দেখে চিনতে পারলাম। এই খামগুলো আমিই লোকমান ভাইকে ঈশরাত আপুর কাছ থেকে এনে বিলি করেছিলাম। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ছড়ানো ছেটানো কাগজগুলো আর কিছু নয়, সব লোকমান ভাইকে লেখা ঈশরাত আপুর চিঠি। লোকমান ভাই শেষ চিঠিটি তুলে আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ল। হাতের তালুতে টিকলিটা ধরে খুব পরখ করে দেখে নিয়ে, তাতে একটা চুমু খেয়ে, বুকের সাথে ছোঁয়ালো। টিকলিটাকে ঈশরাত আপুর শেষ চিঠি দিয়ে গোল করে মোড়ক করলো। তারপর একটা একটা করে চিঠি, সুন্দর করে টিকলি-মোড়কের উপরে আস্তরণ দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে সেটি একটি বেশ বড় সাইজের বাঁধাকপির আকার ধারণ করল। যেন সুন্দর একটা চিঠির বাঁধাকপি।
বলটাকে সে কয়েকটা চুলের ব্যান্ড দিয়ে প্যাঁচালো, যাতে চিঠি গুলো আলগা হয়ে পড়ে না যায়। একটা আজব ঘটনা দেখলাম। চুলের ব্যান্ড দিয়ে প্যাঁচানোর আগে, সে প্রতিটি ব্যান্ডকে নাকের সামনে এনে তার ঘ্রাণ শুঁকে নিল। আমি দেখেছি ঈশরাত আপু ওরকম সব রংধনুর রঙের ব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধত। নিশ্চয়ই ব্যান্ডগুলো সে লোকমান ভাইকে উপহার দিয়েছে। হয়তো ঈশরাত আপুর চুলের ঘ্রাণ লোকমান ভাইকে তার কথা মনে করিয়ে দেয়। গোল বলটাকে একটি পলিথিনের ব্যাগে সুন্দর করে রেখে উঠে দাঁড়ালো। তারপর কচাগাছের মগডালের দিকে তাকিয়ে বেশ আবৃত্তি করে, চীৎকার করে বলতে থাকলো অনেক কথা, কবিতার মতো করে। প্রতিটি কবিতা তার ঠোটস্থ। কবিতাগুলি পড়তে একটুও জড়িয়ে যাচ্ছিল না। শেষ কবিতা পড়েই মাটিতে বসে টমীকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।
শেষের কবিতাটা ছিল,
“প্রিয়তম টমীর বাবা,
আমি মরে গিয়েও বেঁচে থাকব।
তুমিও মরে বেঁচে থেকো।
এই টিকলিটা তোমাকে দিলাম।
জেনো, আমার যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।
তুমি বেঁচে থাকলে অন্তত চোখের দেখাটা দেখতে পাবো।
ইতি,
-শুধু তোমার টিকলি।”
আমিও মনে মনে লোকমান ভাইয়ের আবৃত্তির সাথে সাথে অস্ফুটভাবে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করেছিলাম শেষ চিঠিটা। চিঠিটা যে আমার খুব মুখস্থ।
তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ওখান থেকে চলে এলাম। আমার বন্ধুটির কাছে আসতেই সে বিরক্ত হয়ে বলল,
-‘কিরে তুই কান্তিছিস ক্যান? তোরেও কি ওই টিকলি পরীতি আছর কইরলো নাকি?’
আমি কিছু বলতে পারলাম না। জানি না কেন কাঁদছিলাম। তবে আমার সে কান্না যেন আর থামতেই চায়না। মনে মনে বললাম,
-‘হ্যাঁ আমাকেও টিকলি-পরীতে আছর করেছে। বুকের খুউব ভেতরে, অনেক ভেতরে, কব্জা করে বসে আছে। আর ছাড়বে না কোনোদিন। আমি চাইও না সে টিকলি পরী আমার বুকের মাঝ থেকে আর কোথাও চলে যাক।’
জানো দোয়েল পাখী? ওই দিনটির কথা মনে পড়লেই আমার এখনো চোখ ছলছল করে, কান্না পায়। মনে হয় আমার গলার নলীর মধ্যে কিছু একটা আটকে গ্যাছে। কথা আটকে যায়। সেদিন তাই ফোনে তোমাকে ওভাবে বলেছিলাম যে, ওসব বলতে আমার যে বড়ো কষ্ট হয়। এই যে, এখনই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, প্লিজ!
আর একটা কথা, আমার খুউব ভয় হয়, তুমিও আবার আমার কাছে সেই লোকমান ভাইয়ের “টিকলি-পরী” হয়ে যাবে না তো?
ভালোবাসান্তে,
ইতি,
-শুধু তোমার, বাবুই
লেখক: অমিয় দাশ, ফার্মাসিস্ট, ওষুধ প্রস্ততকারক, বোকা রেটন, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে, amio7@yahoo.com